লেখক : শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ
পৃথিবীতে নানা সময়, নানা দেশে, নানান সাহিত্যকর্ম তৎ তৎ দেশ, কাল এবং শাসনের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে। একথা আমরা জানি। এও জানি যে এতে লেখকের স্বাধীন চিন্তা সর্বদা অবদমিত হয়নি। সমাজে, সংসারে এবং রাষ্ট্রে যে উৎরোল চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছে সাহিত্য। তার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে গিয়েছে। এমনকি শাসনের পক্ষপাতও করেছে।
দস্তয়েভস্কিকে যখন সামরিক ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল তখন তিনি ভেবেছিলেন যে সেই তাঁর জীবনের শেষ। কিন্তু গুলি চলার আগের মুহূর্তে জারের কাছ থেকে নির্দেশ এসেছিল তাঁদের প্রাণদণ্ড রদ করার। বলা হয় জার আসলে মৃত্যুর ভয় দেখাতে চেয়েছিল, খুন করতে চায়নি। এ এক বিচিত্র রাজকীয় রসিকতা, যার মূল্য রাশিয়ার জারেদের একদা দিতেও হয়েছে। কিন্তু দস্তয়েভস্কিকে যেতে হয়েছিল সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে। ফলাফল হয়েছিল ভারী বিচিত্র। একদিকে নিহিলিজমের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন, অন্যদিকে জারের প্রশংসাও করেছিলেন। তাঁর লেখালিখিতে রাশিয়ার জীবন-বাস্তবতার, মানুষের আদর্শ সংঘাতের চিহ্ন যথেষ্ট ফুটে উঠলেও, অমন নিপীড়নাত্মক শাসনের বিরোধিতা আর ফুটে ওঠেনি।
অবিভক্ত বাংলার জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র, সামাজিক সমস্যা ও সংস্কার, প্রেম এবং জীবন সংক্রান্ত লেখালিখি করে গেলেন বেশিরভাগ সময় জুড়েই। সেই তিনিই সাহিত্যিক জীবনের শেষের দিকে এসে রচনা করলেন ‘পথের দাবী’, যা রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করল ব্রিটিশ সরকার। তখনকার সরকারের নানান নথি ঘাঁটলে দেখা যায়, অ্যাডভোকেট জেনারেল, লাটসাহেবের সভার বিশেষ সদস্য কিম্বা চিফ সেক্রেটারি সবাই বলছে ঐ উপন্যাস রাজদ্রোহ, বিপ্লবী চিন্তা, শ্রমিক ধর্মঘট, ব্রিটিশ জনতা ও ক্রিশ্চিয়ানিটির বিরুদ্ধে উস্কানি, বলশেভিজম এবং শাসনের প্রতি বিদ্বেষ জ্ঞাপন করছে। সেই উপন্যাসের প্রকাশক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে উপন্যাস প্রকাশ করে জেলে যাওয়া গৌরবের বিষয় হবে। আর শরৎবাবু বলেছিলেন, জেলে যেন তাঁর গড়গড়াটা নিয়ে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থা দেখে রাখতে। আবার এই উপন্যাস নিয়েই রবীন্দ্র-শরৎ মনকষাকষিও হয়েছিল।
কবে থেকে এই সাহিত্য জগতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ? অথবা রাজনীতি-বিহীন কোনও সাহিত্য কোনকালেই ছিল কি? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে। বিষয়টি বহু প্রাচীন। প্রাচীনকাল থেকেই স্পষ্টভাবে এ ব্যাখ্যাত হতে শুরু করেছিল। আমাদের উপমহাদেশের কথা দিয়েই শুরু করব এ আলোচনা। এই উপমহাদেশে ‘সাহিত্য’ শব্দটি সাম্প্রতিক, যেমন পাশ্চাত্যেও। এখানে আমরা ‘কাব্য’ শব্দটি ব্যবহার করতাম। পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হত ‘পিয়িসিস’ (অ্যারিস্টটলের ব্যবহার গ্রীক ভাষায়)। যদিও কাব্য এবং পিয়িসিস ঠিক একই কথা নয় তবুও এ আলোচনায় তার পার্থক্য নিয়ে বিস্তারিত হবার কারণ নেই। বরং আমরা ফিরে যাই কাব্যের কাছে।
এই উপমহাদেশে প্রাচীন মৌখিক সাহিত্যগুলিকে, যাকে আমরা সাহিত্য বলে তখনও চিহ্নিত করিনি, নানা দেবার্চনা থেকে জাদুর মন্ত্র হিসেবেই চিনেছি, সেখানে কাব্য শব্দটি ছিল না। তখন সূক্ত বলে পদগুলিকে চিহ্নিত করা হত। অনেক পরে কাব্য শব্দটি আসে। কিন্তু এসে যখন পড়ে, তারপর থেকেই তা কেমন হবে তা বাঁধার কাজ শুরু হয়ে যায়।
আমরা আগে নাট্যশাস্ত্রের উদাহরণ থেকে বুঝে নেব কেমন করে বাঁধাবাঁধির কাজটা শুরু হল। নাট্যশাস্ত্র বলছে,
“যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাভা ব্যবস্থিতাঃ।।”
অর্থাৎ বীজ থেকে বৃক্ষ, বৃক্ষ থেকে ফুল যেমন, তেমনই রস থেকেও কাব্যের উৎপত্তি। এবং ‘নহি রসাদ্ ঋতে কশ্চিদ্ অর্থঃ প্রবর্ত্ততে’। অর্থাৎ রস ছাড়া কোনও বিষয়ই (অর্থ) প্রবর্তিত হয় না।
এখন কথা হচ্ছে, রস আর কাব্যের এই সম্পর্কের মধ্যে রাজনীতি কোথায়? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রথমে আমরা নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জেনে নিই। তাহলে প্রাথমিক উত্তর দেওয়া সহজ হয়। নাট্যশাস্ত্রই কাহিনীটি জানাচ্ছে। দেবতারা গিয়েছেন ব্রহ্মার কাছে। মানবসমাজ বা লোকসমাজ অনাচারে পূর্ণ হয়েছে। ধর্মাচার প্রবর্তন করতে ব্রহ্মার কিছু একটা করা প্রয়োজন। ভেবেচিন্তে ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন নাট্যবেদ। যাকে অনেক সময় পঞ্চম বেদও বলা হয়।
মনে রাখা প্রয়োজন যে, বেদের ছান্দস্ এবং পরের সংশোধিত সংস্কৃত বলে পরিচিত ভাষা মুখ্যত ব্যবহার করত উচ্চবর্ণেরা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের শুধু বেদপাঠের অধিকার ছিল। তাও তাদের নারীদের নয়। নারীর সামান্য অংশেরই অধিকার ছিল সংস্কৃততে। রাণী থেকে নগরনটী জাতীয়দের অধিকার ছিল কিছু ক্ষেত্রে। বাকি নারীগণ এবং জনসংখ্যার যে বিপুল অংশ শূদ্র ও দলিত তাদের না-সংস্কৃত না-বেদ, কিছুতেই অধিকার ছিল না। অথচ তারাই সংখ্যাগুরু। সুতরাং ধর্মাচার জানার জন্যও সেই বিপুল সংখ্যাকে নির্ভর করতে হত উচ্চবর্ণের আদেশের বা ব্যাখ্যার।
এই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখব নাট্যশাস্ত্রকে, যেখানে কাব্যের সংজ্ঞায়ন হচ্ছে। নাট্য সকলেই দেখতে এবং শুনতে পারবেন। তাই তার মাধ্যমে ধর্ম এবং নীতিশিক্ষা দেওয়া সহজ। শুরুর দিকে ব্রহ্মা, মুনি ভরত এবং তাঁর একশো মুনি শিষ্যকে শেখাচ্ছেন নাট্যবেদ। তারপরে শিব-পার্বতীর কাছ থেকে লাস্য ইত্যাদি পেয়ে তৈরি হয়ে এঁরা নাট্য দেখাচ্ছেন ব্রহ্মা-সহ দেবতাদের। অসুরেরাও দেখতে এসেছে। সেখানেই প্রথম আমরা স্পষ্ট এক রাজনীতির সূত্রপাত দেখতে পাই। প্রযোজনা হচ্ছে, ‘অমৃতমন্থন’-এর, যাতে দেবতারা অসুরদের বিষ্ণুর সাহায্যে ঠকিয়ে অমৃত নিয়ে নিয়েছিল। দেবতারা তাই অমর, অসুরেরা নয়।
এই নিয়ে লেগে গেল দেবাসুরে দাঙ্গা। দেবরাজ ইন্দ্র, নাট্যস্থলে থাকা জর্জর বা ডাণ্ডা নিয়ে অসুরদের মেরে তাড়ালেন। এরপর থেকে নিশ্চিত করা হল, যে কোনও নাট্যানুষ্ঠানের আগেই জর্জর বা ডাণ্ডাপুজো করতে হবে। একেবারে শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ দেবাসুরের অলৌকিক কাহিনীকে আমরা বাতিল করলেও, নাট্যশাস্ত্রের এই কাহিনী বলে – বিরোধীকে আগেই বুঝিয়ে দিতে হবে যে শাসনের পথ না-মানলে ডাণ্ডা জুটবে। সে নিছক রসময় কাব্য নয়, শক্তপোক্ত মারের ব্যবস্থা।
আরও রাজনৈতিক অবস্থান আছে নাট্যশাস্ত্রের। যেমন মুনিদের শূদ্র হয়ে যাবার কাহিনীটি। মুনিরা কষ্টসহিষ্ণু বলে, দেবতারা তাঁদের এগিয়ে দিয়েছিলেন নাট্যশাস্ত্র শেখার কাজে। সেই মুনিরা, শিখে এবং প্রযোজনা করতে করতে দেবতা ও অন্যান্য ধনবান ভোগী ঋষি-মুনিদের প্রতি বিরক্তি বোধ করছিলেন। সেই নিয়ে তাঁরা ব্যঙ্গ করতে শুরু করলেন নাট্যে। নাট্যশিক্ষাকে ব্যবহার করলেন শাসনে থাকা চর্বি জমে যাওয়াদের বিরুদ্ধেই। ক্রুদ্ধ হল শাসন। ব্রহ্মার কাছে অভিযোগ গেল। ব্রহ্মা শাপ দিলেন যে, এরপর থেকে নাট্যানুশীলনকারীরা উচ্চবর্ণের থাকবেন না, তাঁরা শূদ্র বলে গণ্য হবেন। বর্ণচ্যুতি ঘটল বিদ্রোহীদের। এও সেই নাট্যশাস্ত্রেই লিখিত যেখানে কাব্য, নৃত্য, নৃত্ত, সঙ্গীত, নাট্য ইত্যাদির নন্দনতাত্ত্বিক শাসনতন্ত্র বাঁধা হয়েছে। কাহিনীগুলিতে ব্রহ্মা বা দেবতা ইত্যাদি অলৌকিক হলেও, শাসনের দমন করার এবং নিজের মতকেই শ্রেষ্ঠ বলে চাপানোর ইচ্ছাটি কিন্তু নিতান্ত লৌকিক। সমগ্র নাট্যশাস্ত্র জুড়েই তাই রয়েছে বর্ণবিভাজনের সমর্থন, ব্রাহ্মণাদির অর্চনা এবং যা নাট্যশাস্ত্র বা শাস্ত্র মেনে চলে না সেই জনমানুষের সংস্কৃতির প্রতি নীরব কঠোর ঔদাসীন্য।
পাশ্চাত্যে যখন কাব্যের এবং নাট্যের শাস্ত্র গড়ে উঠল অ্যারিস্টটলের হাতে, তখন কিন্তু সরাসরি ডাণ্ডার প্রয়োগের চাইতে বুদ্ধির প্রয়োগকে গুরুত্ব দেওয়া হল। এর একটা কারণ সম্ভবত এই উপমহাদেশ নাট্যশাস্ত্রের কালেও অনেকাংশেই রাজতান্ত্রিক। আবার গণরাজ্যগুলি তত শক্তিশালী হয়নি। কিন্তু গ্রীসের ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলে রাজতন্ত্র চললেও আথেন্সে এবং স্পার্টায় অভিজাতকেন্দ্রিক গণতন্ত্র ও গণসভা নির্ভর রাজতন্ত্র প্রচলিত। অ্যারিস্টটল, দিগ্বিজয়ী আলেক্সান্ডারের গৃহশিক্ষক হলেও, গণতন্ত্রের কথা ভোলেননি। তাই বুদ্ধির আশ্রয় নিলেন।
কী করলেন? সোজা কথায় বলি তা। প্লেটো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন নাট্য এবং তার শিল্পীদের নিয়েও। কারণ তাঁরা প্রচলিত দিওনিসিও উৎসবের রাষ্ট্রস্বীকৃত যে কোরাসের কাঠামো তার বাইরে ক্রমে সরে যাচ্ছিলেন, নানা স্বাধীনতা নিয়ে। তাঁরা কোরাসের বাইরে মুখ্যচরিত্র বা প্রোটাগনিস্ট সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। যে কোরাসের সঙ্গে সংলাপে লিপ্ত হতে পারে, নানা স্বাধীন মতামত দিয়ে। আস্তে আস্তে ডিউটারোগনিস্ট, ট্রেটাগনিস্টও চলে এসেছিল। এতে একটি আদর্শ রাজ্যে বা রাষ্ট্রে সমস্যা হবে। শিল্পের এত স্বাধীনতা থাকলে চলে না।
কিন্তু অ্যারিস্টটল একেবারে ভিন্ন রাস্তায় হাঁটলেন। তিনি বললেন, দর্শক তার এম্প্যাথিয়ার মাধ্যমে, অর্থাৎ প্রোটাগনিস্টের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করার মাধ্যমে প্রোটাগনিস্টকে নিজের সক্রিয় ভাবনার ক্ষমতা অর্পণ করে দেয়। প্রোটাগনিস্টের আবেগকে নিজের আবেগ বলে বোধ করে। প্লেটো এতে ক্ষিপ্ত হলেও অ্যারিস্টটল জানালেন এই দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রথমে প্রোটাগনিস্টকে একটা জমকালো সাফল্য দেওয়া যাক। যেমন, ইডিপাস রেক্স নাটকে প্রোটাগনিস্ট ইডিপাস থিবাই-এর রাজা হয়ে পেয়েছিল। দর্শক, ইডিপাসের মত করেই তা উপভোগ করুক। পিতৃহত্যা এবং মাতৃশয্যায় লিপ্ত হবার মত কাজ করলেও, দর্শক প্রথমে একে উপভোগ করুক। এরপরে নাট্যের মধ্যপর্যায়ে আসবে ইডিপাসের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হওয়া। ততক্ষণে দর্শক ইডিপাসের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে ফেলেছে। অতএব নাটককার এবং নাট্যপরিচালক তথা শাসনের হাতের মুঠোয় এসে গেছে।
কেমন করে? সহজ পদ্ধতিতে। এই যে ভাগ্যের বিপরীতগতি, একে পেরিপাটাইয়া বলা চলে। এইটা নাট্যকে নিয়ে যাবে প্রোটাগনিস্টের জন্য চূড়ান্ত এক বিপর্যয়ের মধ্যে। যে বিপর্যয়কে ক্যাটাস্ট্রোফি বললেন তিনি। বললেন এই বিপর্যয় দেখে দর্শক পাবে ক্যাথারসিস। তা কী? তা হল বিশোধনের প্রক্রিয়া। যে ভুলটি, যাকে হামার্তিয়া বলা হচ্ছে, যা প্রোটাগনিস্ট করেছে, সেই ভুলই তাকে আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু তার যা পরিণাম হল তাতে দর্শকের যে আবেগ জেগেছিল সেই আবেগ ম্লান হয়ে যুক্তি জেগে উঠবে। সেই যুক্তি, দর্শকের পূর্বেকার আবেগকে বহিষ্কার করবে। এইসব করার জন্য শুধু প্রোটাগনিস্টকে নাট্যে তার ভুলস্বীকার বা অ্যানাগনোরেসিস করতে হবে। তাহলেই দর্শকও তারই সঙ্গে তার নিজের মনে জন্মানো ভুল সম্পর্কে অনুতপ্ত হবে এবং বিশোধিত হবে। এই হল মোটা দাগে অ্যারিস্টটলের ‘আর্স পোয়েটিকা’ বা পোয়েটিক্স। দু’হাজার বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে এ শাসন করছে শিল্পের সব শাখাকে একরকম। অর্থাৎ সাহিত্যও, আধুনিক জীবনে যখন এসেছে, খানিক একে মেনেই চলেছে।
প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বলে কথিত দুটি ভূখণ্ডে আমরা দেখলাম কেমন করে প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্য শাসনের রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এবারে আমরা চলে আসব আধুনিক সময়কালে। অ্যারিস্টটল কাব্যের সত্য বা সাহিত্যের সত্যের সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন তাকে সম্ভাব্য সত্যের কথা বলতে হবে। সে-কথা বলতে গিয়ে আবার বলছেন সেই সম্ভাব্য সত্য যেন অযৌক্তিক না-হয়। অ্যারিস্টটল এবং তাঁর অনুবর্তীদের মত, ব্রিটিশদের হাত ধরে আমাদের উপমহাদেশেও পৌঁছেছিল। এবং বঙ্কিমচন্দ্রদেরও প্রভাবিত করেছিল।
বঙ্কিম ‘উত্তরচরিত’ সমালোচনায় বলছেন, ‘যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই’। আরেক জায়গায় বলছেন, ‘যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি’। বঙ্কিমের আরেকটিও প্রসিদ্ধ কথা আছে। ‘যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।’ ‘বাঙ্গালীর নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন/ বিবিধ প্রবন্ধ’-তে এই উক্তি পাচ্ছি। এবারে দেখার বিষয় হচ্ছে বঙ্কিম যা-বলছেন তা স্বয়ং কেমন করে মানছেন বা আদৌ মানতে পারছেন কি না!
বঙ্কিম যখন ‘আনন্দমঠ’ লিখছেন তা ইতিহাসনির্ভর হলেও সত্যিকারের ঐতিহাসিক উপন্যাস কি? আনন্দমঠে, ইতিহাসের প্রতিকৃতি কি আঁকলেন? নাকি তার অতিরিক্ত কিছু করলেন? করলে তার উদ্দেশ্য কী? বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। ইতিহাস যা বলে তা বঙ্কিমের উপন্যাস বলে না। ইতিহাস বলে ফকির এবং সন্ন্যাসীরা মিলিত হয়েছিলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তাঁদের নানা অধিকার কেড়ে নেওয়ার ক্রোধে। ইতিহাস এও বলে সন্ন্যাসী ফকিরে দ্বন্দ্বও হয়েছে। কিন্তু ফকিরেরা এই বিদ্রোহকে সন্ন্যাসীদের থেকেও অনেক বেশি সময় ধরে চালিয়ে গেছিলেন।
বঙ্কিম, গ্লিগের ‘মেমোরিজ অব দ্য লাইফ অব ওয়ারেন হেস্টিংস’ এবং হান্টারের ‘এনালস অব রুরাল বেঙ্গল’ থেকে কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করে একে ঢেলে সাজালেন তাঁর তৎকালীন মতাদর্শ অনুযায়ী। যে বঙ্কিম একদা পাশ্চাত্যের সাম্যের দর্শন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন সেই বঙ্কিম সরে গিয়ে ততদিনে নূতন বঙ্কিম জন্ম নিয়েছেন, যাঁর মূল প্রকল্প হল হিন্দু-পুনরুত্থানবাদ, হিন্দু ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। অতএব এই উপমহাদেশে পরে আগত ইসলাম এবং ইসলামধর্মীয় সমাজের প্রতি তাঁর একটি বিদ্বেষ প্রকাশ পেল এতে। উল্টোদিকে থাকল, নবীন ইংরাজ রাজত্বকে স্বাগত জানাবার ইচ্ছা। তাঁর সন্তানদল সেই ইংরেজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই যুদ্ধ করল। কারণ, ততদিনে বঙ্কিম-মানসে এবং সমকালীন হিন্দুসমাজের বুদ্ধিজীবী অংশে একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে একরকম। তা হল, পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানান্দোলনের ফলে উদ্ভূত যাবতীয় বিকাশের সুফলের সঙ্গে বা তার বস্তুবাদের উন্নত চেহারার সঙ্গে প্রাচ্যের আধ্যাত্মবাদী ধর্মীয় ঐতিহ্যের মিশেল ঘটলে ভারতীয় সমাজে প্রকৃত আধুনিকতা আসবে। তখন ইংরেজের শাসনের প্রয়োজন থাকবে না।
রবীন্দ্রনাথ একদা ‘ব্যক্তি প্রসঙ্গ’-তে এই বকচ্ছপ ধারণাটির ‘আনন্দমঠ’ জাতীয় রূপ নিয়ে লিখেছিলেন কতগুলি কথা। লিখেছিলেন : “এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী, সীতারাম, একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্যে নয়, উপদেশ দেবার জন্যে। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরবগর্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার করে বসল।
আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যরসের আদর সে নয়, দেশাভিমানের। এক-এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা ধর্মসাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে থাকে সেই সময়টা সাহিত্যের পক্ষে দুর্যোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানো চলে। শুঁট্কি মাছের প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশি হয় তা হলে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। ওই জিনিসটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না। সাময়িক সমস্যা এবং চল্তি সেন্টিমেন্ট, সাহিত্যের পক্ষে কচুরিপানার মতোই, তাদের জন্যে আবাদের প্রয়োজন হয় না, রসের স্রোতকে আপন জোরেই আচ্ছন্ন করে দেয়।”
এইখানে সাহিত্যের যে রাজনীতি তা যে বঙ্কিম আর রবীন্দ্রে পৃথক হয়ে গেছে, এইটা বুঝতে আমাদের আর অসুবিধে হয় না। নব্য হিন্দুত্বের সনাতনী ধ্বজার প্রতি বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের যে আস্থা স্থাপিত হয়েছিল তার থেকে ততদিনে তিনি ঢের দূরে সরে গিয়েছেন। বঙ্কিম স্বভাবাতিরিক্ত আনলেন এবং প্রকৃতির অনুকৃতি বাদ দিয়েই এই সকল সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। কিন্তু সেই অতিরিক্তটি তাঁর প্রচারকসত্ত্বার অতিরিক্তপনা। ধর্মোন্মত্ততায়, রাজনীতি উন্মত্ততায় তার কদর থাকলেও সাহিত্যজগতে তা থাকার কারণ ছিল না। একটি নির্দিষ্ট সময় এবং মানসিকতার কাছে তার আবেদন। তারপরে তার প্রয়োজন যায় ফুরিয়ে।
এই যে সাহিত্যের রাজনীতি এবং সাহিত্যিকের রাজনীতি দুটোকেই রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। ফলে নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন। বঙ্কিম তাঁর আগে বলে বঙ্কিমের সমালোচনার মধ্যে দিয়েও নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। বঙ্কিমের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ নিয়ে তাঁর দীর্ঘ সমালোচনা আছে। সেখানে দেখব তিনি সমালোচনার শুরুতেই নব্যহিন্দু জাতীয়বাদের ধুয়োকে স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করছেন সমস্যা হিসেবে। এই রাজনীতিতে অন্যান্য অনেক কিছুর মতই বঙ্কিমের সাহিত্যিক যোগদান প্রবল। সে হল সাহিত্যিকের রাজনীতি। বঙ্কিম ‘কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্’ বলে লিখছেন, ‘জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।’
হিন্দুসমাজে যখন ধর্মান্দোলন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, তখন তিনি কৃষ্ণ চরিত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এ কথাও জানাচ্ছেন লেখায়। কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য না-হলেও সামান্য ক’টি কথা বলা প্রয়োজন। কৃষ্ণের বাল্যের ননীচুরি, রাধা সমেত গোপিনীদের সঙ্গে যৌনতা, মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে কূট এবং ক্রূর কৌশলে জরাসন্ধ, দ্রোণ, দুর্যোধন ইত্যাদি হত্যার যে সকল কাণ্ডকে তিনি বাদ দিতে চেয়েছেন সেই সব অংশ বাদ গেলে রক্তমাংসের মানুষ আর পড়ে থাকে না। পড়ে থাকে, নির্দিষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে মানুষের আদর্শের একটি কাঠামো। তা সাহিত্যরসশূন্য হতে বাধ্য। প্রচলিত মহাভারতের পাঠ কিন্তু জানায় প্রাথমিক রচকেরা, এমন রসহানির কথা ভাবতেও চাননি। তাঁরা সকল চরিত্রকেই দোষে-গুণে মানবিক করে এঁকেছেন। পরের কালে নানা হস্তাবলেপে অনেক অলৌকিক কাণ্ডাদি দিয়ে ঈশ্বরাবতার সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে বটে, মূল কাহিনীতে তা ভাল করে এঁটে বসেনি। এবং রবীন্দ্রনাথ এর সমালোচনা করার সময় এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বিশেষ করে তাই উল্লেখ করেছিলেন। সেইটা আবার রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি।
সেই রাজনীতি আবার বঙ্কিমের দেশাভিমান তথা হিন্দুত্বের অভিমানের বিরুদ্ধে চলার রাজনীতি। তার ফলে এই হিন্দুত্বের অভিমান বিপ্লববাদী আন্দোলনকে যে-পথে নিয়ে গেল, কিম্বা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকেও হিন্দুত্বের পরিসরে আবদ্ধ করে ফেললো, তার বিরোধে সক্রিয় হল রবীন্দ্রনাথের কলম। ‘চার অধ্যায়’ আর ‘ঘরে-বাইরে’ তার মূর্তরূপ। এমনকি ‘গোরা’ সম্পর্কেও একথা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ, মানুষকে হিন্দু-মুসলমান-ইংরেজ নয়, মানুষ হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তারই ফলে তিনি সন্দীপের হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে, নিখিলেশের মুসলমান প্রজাদের প্রতি হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তারই ফলে তিনি আবার ব্রাহ্মণ পরিবারে মানুষ হওয়া ইংরাজ সন্তান গোরার ব্রাহ্মণত্বের অভিমানকে ভেঙে তাকে টেনে এনেছিলেন দেশের সেই সীমানায় যেখানে মানুষ বস্তুত মানুষই। ধর্ম, জাত, বর্ণ ইত্যাদি তার পরিচয় নয়। একইভাবে বিপ্লববাদের যে হিংসার পথ সে হিংসা যে আসল উদ্দেশ্য সাধনে অক্ষম হয়ে শুধু মানুষের অপরিসীম শক্তিকে ক্ষয় করে চলেছে, সে ছবিও, সেই সময়েই তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি। প্রবল সমালোচনা এসেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই, সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে। কিন্তু তিনি তাঁর অবস্থান বদল করেননি।
এই প্রসঙ্গেই আবার বঙ্কিম-রবীন্দ্রে ফিরে যাই একবার। বঙ্কিম ছিলেন ইংরেজ শাসনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই ডেপুটিগিরি তাঁকে অন্ন জুগিয়েছে এ যেমন সত্যি, তেমনই আবার কলমকেও আটকেছে ইংরাজবিরোধী হতে। আবার রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জমিদারী ছিল। অন্যদের মতন তাঁকে অন্নচিন্তা করতে হয়নি তেমন করে। শুরুর জীবনে ‘বড় ইংরেজ’ ‘ছোট ইংরেজ’ করে স্পষ্ট ইংরেজ-বিরোধ করে ওঠেননি। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর, যখন প্রায় সমস্ত ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বরা, প্রতিবাদ বা আন্দোলন করার পথকে কৌশলে পরিহার করেছেন প্রথমে, তখন তিনিই রাতারাতি একক সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ ‘নাইটহুড’ ত্যাগ করেছিলেন। ব্রিটেনের রাজগৌরবকে আঘাত করাকে ব্রিটিশরা ভাল ভাবে নেবে না, জমিদারীর ক্ষেত্রেও আঘাত আসতে পারে জেনেও কিন্তু ঐ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ শুধু অন্নচিন্তাই সবক্ষেত্রে সাহিত্যিককে আপ্লুত করে রাখে না, নিজ চেতনার সম্মান বা প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানবিরোধীতার তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টিও সচেতন করে রাখে, একথাও ভাবার।
ভেবেছিলেন শরৎচন্দ্রও। চিত্তরঞ্জন, যিনি দেশবন্ধু হিসেবে পরিচিত ইতিহাসে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানেই শরৎচন্দ্রের রাজনীতিতে সক্রিয় যোগদান। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কংগ্রেসে থাকাকালীনই তাঁর সঙ্গে বাংলার বিপ্লববাদীদের যোগাযোগ দৃঢ় হয়। তাঁদের মনোভাব বা মতাদর্শকে তিনি বোঝার চেষ্টা করেন। তার ফলাফলে লিখলেন ‘পথের দাবী’। শুরুতেই লিখেছি তার সম্পর্কে ইংরেজ শাসনের মনোভাব। এবারে আমরা এই বিষয়ে রবীন্দ্র-শরৎ বিনিময়ের আগে দেখে নেব এই উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্য সমকালের কাছে কেমন ছিল!
ফরওয়ার্ড পত্রিকা লিখেছিল, মাস্টারক্লাসের সাহিত্য। কিন্তু সে নিজেই ছিল সরাসরি রাজনৈতিক কাগজ। সুভাষ-শরৎ, দুই বসু ভাইয়ের কাগজ, যা বিপ্লববাদীদের এক বড় অংশকে নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গড়ে তুলেছিল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সেখানে ঐ সমালোচনা ছিল কারণ বিপ্লববাদী আন্দোলন নিয়ে ঐটিই বিপ্লববাদীদের পক্ষের লেখা। ‘চার অধ্যায়’ রবীন্দ্রনাথ বিপ্লববাদের আদর্শের এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার অন্ধত্বের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। অতএব বিপ্লববাদীদের স্বপক্ষের লেখা ‘পথের দাবী’-কে তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু অন্যরা?
আনন্দবাজার নিষিদ্ধকরণের বিরোধ করেছে। অন্যান্যরাও করেছে। অমৃতবাজার একে বিশেষ সাহিত্যমূল্য দিতে চায়নি। বরং নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার উপন্যাসটির মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে এমনই অভিমত জানিয়েছিল। সত্যিই তাই একদিকে। বাজেয়াপ্ত হবে জানা ছিল বলে ছাপা হতেই একদিনের মধ্যে নানা জায়গায় বই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনগুণ মূল্যেও বই বিক্রি হয়েছে। হাতে লেখা কপি পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। আর বিপ্লবীরা নানা প্রেসে অজ্ঞাতভাবে ছাপিয়েছেন সেকালে এই বই। মলাট ছাড়াই দেদার বিক্রি হয়েছে। তবু সাহিত্যমূল্যের প্রশ্নে শরৎচন্দ্র সমালোচিত হয়েছেন।
অর্চ্চনা পত্রিকাতে কেশবচন্দ্র গুপ্ত জানিয়েছিলেন বইটি বিলুপ্ত হয়ে শরৎবাবুকে একপ্রকার নিস্তার দিয়েছে। কারণ নায়ক সব্যসাচী অতিমানব। তাঁর আবেগ নেই, বে-আক্কেলী ভূতুড়ে জীব তিনি, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম ইত্যাদি কোমল বৃত্তিও তাঁর নেই, আছে শুধু হিংসা ব্রিটিশের প্রতি। ব্রিটিশ বিদ্বেষের উপন্যাসে বর্ণিত কারণ তাঁর এক দাদাকে বন্দুকের লাইসেন্স দেয়নি ইংরেজ, তাই ডাকাতের হাতে তিনি মারা যান। এই কারণ দেশপ্রেম ইত্যাদি নয়। অর্থাৎ কেশবচন্দ্র মুখ্য চরিত্রকে নস্যাৎ করার মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্রের লেখাকে আজগুবি বলেছেন।
সেখানেই ক্ষান্ত হন’নি। কয়েকটা পাতা, যেগুলো সরকার বিরোধী গরম বক্তৃতার সংকলন বলে তিনি মনে করেছেন, সেই পাতাগুলোকে বিষ দাগিয়ে ছেড়ে দিলেই উপন্যাসের হাল আরো করুণ হত। সেকালের আজগুবী গোয়েন্দা গল্পের লেখক পাঁচকড়ি দে-র বিপুল বিক্রি ছিল। বস্তুত সাহিত্যরসের বালাই-ও ছিল না তাতে। তার ঘটনাবলীও সুস্থির পাঠকের কাছে হাস্যকর রকমের অসহ। যদিও পাঁচকড়িবাবু তাঁর উপন্যাস রবীন্দ্রনাথকেও উৎসর্গ করেছেন, তথাপি সাহিত্যাকাশে তাঁর স্থান হওয়ার ছিল না। হয়ওনি। সেই পাঁচকড়ি দে-র উপন্যাসের সঙ্গে ‘পথের দাবী’-র তুলনা করেছিলেন কেশবচন্দ্র। এতটাই তাচ্ছিল্য ছিল ঐ উপন্যাসের প্রতি।
তাহলে আমরা আরেকটি প্রশ্নেরও সম্মুখীন হচ্ছি, যে সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকের রাজনীতি রচনার সাহিত্যমূল্যকে বৃদ্ধি করে কি না! সে প্রশ্নে যাবার আগে আমরা রবীন্দ্র-শরৎ আদানপ্রদানের প্রসঙ্গটিকেও একটু আলোচনা করে নিই। ‘পথের দাবী’ নিষিদ্ধ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে বইটি পাঠিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। চেয়েছিলেন নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করুন রবীন্দ্রনাথ।
রবীন্দ্রনাথ, নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করেননি। বরং ইংরেজ রাজশক্তির ক্ষমাশীলতা অন্যান্য দেশের রাজশক্তির চাইতে বেশী একথাই জানিয়েছিলেন। এও জানিয়েছিলেন, রাজশক্তির বিরোধিতা করতে গেলে মেনে নিতে হবে তার ফলে ঘটা যাবতীয় কিছুকেই। লিখেছিলেন : “শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা । অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হ’ত না। আমরা রাজা হলে যে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে- শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে–রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে ।” শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইতে প্রস্তুত থাকতে হয়। সে আঘাত নিয়ে বিলাপ করা সে আঘাতের মূল্যকে মাটি করে দেয়, এও লিখেছিলেন। অবশ্য শরৎচন্দ্রের স্বপক্ষেও লিখেছিলেন, যে তিনি শরৎচন্দ্র, যাঁর লেখা আবালবৃদ্ধবনিতা পড়েন এবং ভালবাসেন। তাই তাঁর লেখাকে ব্রিটিশ সরকার তুচ্ছ করতে পারেনি। সেকারণেই এই বই-এর উপর নিষেধাজ্ঞা। এ একধরণের ব্যাজস্তুতিও। কিন্তু ‘পথের দাবী’-র সাহিত্যিক মূল্য রবীন্দ্রনাথ দেননি স্পষ্টতই। সে বিষয় কোনো কথাই প্রায় নেই তাঁর চিঠিতে।
যা স্পষ্ট হচ্ছে এসব থেকে তা-হল রাজনৈতিক উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য নির্ধারণ করাটা কঠিন কাজ। কারণ যে কোনো রাজনৈতিক মতের প্রতিপক্ষ থাকবেই। বস্তুত পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বহীন রাজনীতি হয় না। যেহেতু হয় না, সেই কারণেই রচনার রাজনীতি যে পক্ষের অনুবর্তী হবে, সেই পক্ষ উচ্চ প্রশংসা করবে। কিন্তু যাদের বিপক্ষে যাবে, তারা নিন্দা করবে। সমালোচিত হওয়ার কাজটা এক্ষেত্রে হওয়া মুশকিল। লেখকের দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁরও রাজনৈতিক ভাবনার দায় থেকে যেহেতু প্রেরণা এসেছে, তাই বহুক্ষেত্রেই উপন্যাস-গল্প বা কবিতা ইত্যাদি শ্লোগানধর্মী হয়ে দাঁড়ায়। অথবা নিছক প্রচারধর্মীতা গ্রাস করে রচনার বৃহদাংশকে। সেক্ষেত্রে সাহিত্যিক মূল্যটি কমে আসে। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করার কাজটি কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।
সাহিত্যের রাজনীতি সমাজ এবং রাজ্য বা রাষ্ট্রশাসন থেকে জন্মায়। সাহিত্যিকের রাজনীতি? আনাতোল ফ্রাঁস-র মতে সাহিত্যিক একাধারে দন কিহোতে এবং সাঙ্কো পাঞ্জা।
দন কিহোতে বলছেন, “মহৎ বিষয়ের কথা চিন্তা করো। প্রকৃতিকে তুলে ধরো তোমার নিজের মাপে আর সমস্ত বিশ্ব জগৎ হোক তোমার অপরাজেয় আত্মার সমান ছাড়া আর কিছু নয়। সম্মানের জন্য সংগ্রাম করো; একমাত্র তাই-ই মনুষ্যত্বের উপযুক্ত; আর যদি তোমার ভাগ্যে জোটে নির্যাতন, আঘাত, তবে হাসিমুখে পবিত্র শিশিরবিন্দুর মতো তোমার রক্ত ঝরুক।”
দন তো মধ্যযুগের নাইটদের মতন শিভালরির লক্ষ্যে অবিচল। নানা কল্পিত শত্রুদের তিনি তাঁর রুগ্ন ঘোড়া আর সামঞ্জস্যহীন যুদ্ধসাজেই দমন করবেন তরবারির সাহায্যে। তা করতে গিয়ে অথবা প্রেমের জন্যও যদি তাঁর জীবনান্ত হয় তাহলেও তাঁর কাছে তা মহান কাজ। কিন্তু অনুচর সাঙ্কো তো প্রভুটির মতন নন। তিনি আমাদের চলতি কথায় উচ্চ আদর্শের স্বপ্নময় জগতের বাইরে বাস্তববুদ্ধিধারী মানুষ। তিনি কী বলছেন?
তিনি বলছেন, “যেমনটি আছো তেমনটি থাকো, বন্ধু। শুকনো রুটির টুকরো যা পাও তাই খেয়ে খুশী থাকো। প্রভুকে মান্য করো, তিনি বিচক্ষণ বা নির্বোধ যা-ই হোন না কেন। বেশী জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। মারের ভয়টা মনে রেখো। বিপদের ঝুঁকি নিও না।”
ফ্রাঁস-র কথামতন আমরা কখনো কিহোতে হই, কখনো সাঙ্কো। কখনো কিহোতের মত জগৎ উদ্ধারে ব্যপ্ত হতে চাই, কখনো সাঙ্কোর মতন আমদানি নিয়ে মাথা ঘামাই। বেশীরভাগ সময়, বিশেষ করে আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের সাঙ্কো সত্ত্বাই জয়ী হয়, যদিও আমরা দন কিহোতেকে শ্রদ্ধা করি। এই উপমহাদেশে রাজনীতির নানা ঢেউ, নানা আন্দোলন, নানা উত্থান-পতন এসেছে, ঘটেছে। বারংবার আশা তৈরী হয়েছে। আশাভঙ্গও হয়েছে তার দ্বিগুণ-ত্রিগুণ অভিঘাতে। ফলত লোকসমাজ এভাবে ভাবতে শুরু করেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সাঙ্কোকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছি বা নিচ্ছি। ইউটোপিয়ার স্বপ্নভঙ্গের চাইতে সাবটোপিয়ায় রুটির সঙ্গে মাখন আমাদের সাহিত্যিক দিগ্বিজয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
একে আরেকটু ভেঙে বললে, আমরা রাজনৈতিক রুচিতে সরে চলেছি ক্রমাগত প্রতিষ্ঠানের দিকে। সাহিত্যিক ক্রমাগত ছিন্নভিন্ন হচ্ছেন একদিকে পেটের তাগিদ অন্যদিকে শিল্পের তাগিদের টানাপোড়েনের মধ্যে। আমরা যে-ধরণের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বসবাস করি তাতে এ টানাপোড়েন থেকে খুব সাম্প্রতিক কালে কেন, দূর ভবিষ্যৎ-এও মুক্তির আশা নেই। তাহলে সাহিত্যিক কোন রাজনীতিকে ধারণ করবেন? প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র ইত্যাদির? না তার বিপরীত রাজনীতিদের? এর কোনও সর্বজনীন উত্তর কোনকালেই ছিল না। আজ-ও নেই। ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যিককেই নির্ধারণ করতে হবে তাঁর চলনপথ, সে পথের দায়-দায়িত্ব ভাল-মন্দ সমেত। সেই নির্ধারণই আবার তাঁর কালাতিক্রমী হবার সম্ভাবনা থাকা না-থাকার বিষয়টিকেও নির্ধারণ করবে।
লেখক পরিচিতি : শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ
গত শতকের সাতের দশকে জন্ম। মফস্সল ও কলকাতায় বড় হওয়া। ছাত্রজীবনেই নাটক ও চলচ্চিত্রের সাথে জড়িয়ে পড়া এবং লেখালিখির সূত্রপাত। কাজ করেছেন দূরদর্শন, ইটিভি এবং আকাশ বাংলায় নির্মাতা ও সংবাদকর্মী হিসেবে। বর্তমানে লেখা, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত। নানা সংস্থায় ও কলেজে নাট্য, চলচ্চিত্র ও স্থিরচিত্র ইত্যাদি বিষয়ে আংশিক সময়ে আমন্ত্রিত শিক্ষকতা করেন। প্রকাশিত বই - মহাভারত (১-১০ খন্ড), ভীষণ গোপনে বেঁচে আছি (কবিতার বই), রঙ্গমঞ্চ (গিরিশ-শিশির-অহীন্দ্র যুগের বাংলা নাট্যমঞ্চ এবং চলচ্চিত্র নিয়ে), ঘৃণার সীমান্তে, ধর্মযোদ্ধা রাম, মিথের সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যের মহাকাব্য, ব্যাবিলন থেকে ভাইকিং, জলের প্ৰতিভা, অগ্নিযুগ, গোলাপবালা বাই লেন ইত্যাদি।
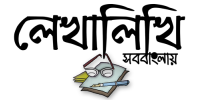
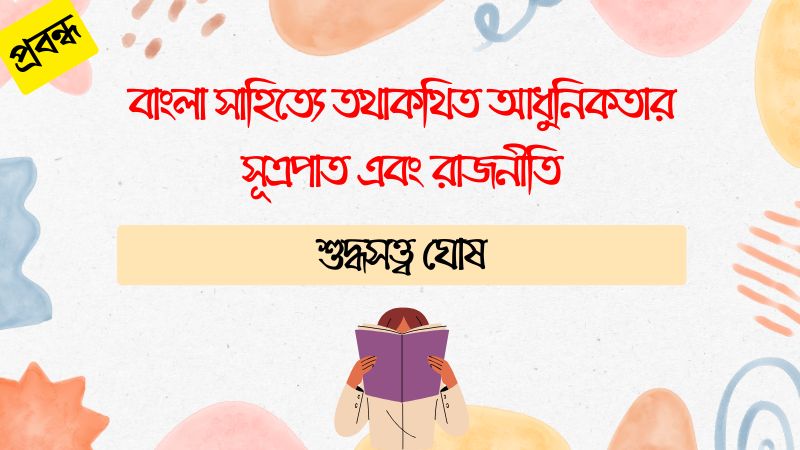

লেখাটি অবশ্যই তত্ত্ব,তথ্য এবং বৌদ্ধিক উত্তোরণের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো অনেকেই নানা লেখকের নানা লেখা পড়ে এই লেখকের ভাবনার কিছু কিছু সঙ্কেত ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। এই ধরনের মনস্ক পাঠকও নিশ্চয়ই মানবেন যে, নাতিদীর্ঘ রচনায় এতগুলি দিক সংহত করে লেখক এখানে যে ভাবে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করেছেন তা পাঠকদের সমৃদ্ধ করবে।সহমত বা দ্বিমত, যে পাঠক যে অবস্থান নিন না কেন তাঁকে যুক্তি র গভীর পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে।
রতন চক্রবর্তী।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, রতনদা!
খুব সুন্দর লেখা। এই রকম লেখা পড়ে পাঠক সমৃদ্ধ হোক।