“দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনাশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।।”
‘দুর্গা’ শব্দটিকে ভেঙে বলা হচ্ছে_ ‘দ’ অক্ষর দৈত্যনাশক, ‘উ-কার’ বিঘ্ননাশক, ‘রেফ’ রোগনাশক, ‘গ’ অক্ষর পাপনাশক এবং ‘অ-কার’ ভয়- শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই ‘দুর্গা’। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে, ‘দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা’ অর্থাৎ দুর্গ নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্য দুর্গা নামে অভিহিত।
দেবী দুর্গা সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে পুরাণে উল্লেখ আছে- মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতারা ব্রহ্মার শরণ নিলে ব্রহ্মা, শিব ও অন্য সব দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে আসেন। নিজেদের দুর্দশার কথা জানিয়ে ব্রহ্মার কাছে জানতে চান, এ থেকে পরিত্রাণের পথ কী? স্বয়ং ব্রহ্মার দেওয়া বরেই মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না কোন পুরুষ। তখন বিষ্ণুর নির্দেশে সব দেবতার থেকে যে দেবীর জন্ম হয় তিনিই ‘দুর্গা’। পুরুষদের অবধ্য মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন দেবী দুর্গা। প্রথমবার অষ্টদশভূজা উগ্রচন্ডীরূপে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দশভূজা দুর্গারূপে।
দুর্গা, মহিষমর্দিনী, শূলিনী, পার্বতী, কালিকা, ভারতী, অম্বিকা, গিরিজা, বৈষ্ণবী, কৌমারি, বাহারী, চন্ডী, লক্ষ্মী, উমা, হৈমতী, কমলা, শিবানী, যোগনিদ্রা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা প্রভৃতি নামে ও রূপে দুর্গা দেবী পূজিত হয়ে থাকেন।
দেবী দুর্গা সাধারণত দশভূজা, তবে শাস্ত্রানুসারে তার বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোলো, আঠারো বা কুড়ি। প্রতিমার রঙ হতে পারে অতসীপুষ্পবর্ণ বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কখনও বা রক্তবর্ণ। প্রতিমা ছাড়াও পূজা হতে পারে দর্পণে, অনাবৃত ভূমিতে, পুস্তকে, চিত্রে, ত্রিশূলে, শরে, খড়গে বা জলে।
পৌরাণিক উপাখ্যান :
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লিখিত কিংবদন্তি অনুসারে দুর্গোৎসবের প্রবর্তক স্বয়ং কৃষ্ণ। এখানে বলা হয় কৃষ্ণ সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা করেন। দ্বিতীয়বার দুর্গার আরাধনা করেন মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয়ের ভয়ে ভীত ব্রহ্মা। ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে সংকটাপন্ন মহাদেব তৃতীয়বার দুর্গাপূজা করেছিলেন। এরপর দুর্বাসা মুনির শাপে শ্রীভ্রষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যে দুর্গাপূজা করেন, তা ছিল চতুর্থ দুর্গোৎসব। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মুনিগণ, সিদ্ধ ও দেবতাগণ এবং মানবগণ নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গোৎসবের আয়োজন করে।
তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং লোকমান্য কাহিনীটি রয়েছে দেবীমাহাত্ম্যম-এ। বাংলায় সাধারণত শ্রী শ্রী চন্ডী নামে পরিচিত সাতশত শ্লোকবিশিষ্ট এই দেবীমাহাত্ম্যম পাঠ দুর্গোৎসবের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও বটে। এই গ্রন্থে চারটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে; যার মধ্যে একটি কাহিনী দুর্গোৎসব প্রচলনের এবং অন্য কাহিনীগুলো দেবীর মাহাত্ম্যগাথা। যেমন- রাজা সুরথের কাহিনীতে দেখা যায় তিন বছর কাল দুর্গার পূজা করে তিনি হারানো রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। অন্য কাহিনীগুলো হলো- মধুকৈটভের কাহিনী, মহিষাসুরের কাহিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভের কাহিনী।
দুর্গাপূজার উপাচার :
ঘরে বা মন্দিরে হোক একটি পূর্ণাঙ্গ পূজায় একাধিক উপাচার বা পূজাদ্রব্য উৎসর্গ করার প্রথা রয়েছে। যদিও অঞ্চল, সম্প্রদায় বা সময় ভেদে এই উপাচারগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে যে কোন পূজায় দুটি বিষয়ের প্রাধান্য থাকে-মন্ত্র ও উপাচার এবং অন্তর ও বাহ্য দিক। মন্ত্র হচ্ছে মনের বিষয়। আর সহজভাবে বলতে গেলে উপাচার হচ্ছে উপকরণ। যে পূজায় ষোড়শ উপাচার, মহাস্নান, বলি ও হোম থাকে সেটাই হলো মহাপূজা। মহাপূজায় ষোড়শ উপাচার বিধেয়। এগুলো হলো
আসন (স্বর্ণাসন, বস্ত্রাসন, কাষ্ঠাসন, কুসাসন)
অর্ঘ্য (আতপ চাল, তিল, জল, দুধ, কুশাগ্র, দই, যব ও শ্বেতসরিষা)
আচমনীয় (কর্পূর কিংবা সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত জল)
অষ্টকলসি স্থানীয় জল (তেত্রিশ প্রকার জল, যেমন- শুদ্ধজল, গঙ্গাজল, সুগন্ধিজল, পুষ্পজল ইত্যাদি)
ভূষণ (নয় অঙ্গে- চরণ, কটি, বক্ষ, হস্ত, কণ্ঠ, নাসিকা, কর্ণ, সীমন্ত ও মস্তক)
স্বাগত, পাদ্য (পা ধোয়ার জল), বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মালা, বিল্বপত্র ও চন্দন।
সপরিবারে দুর্গা, কে-কীসের প্রতীক :
দেবী দুর্গার বাহন হচ্ছে সিংহ। দুর্গোৎসবে সিংহেরও পূজা কর্তব্য বলে গণ্য হয়।
প্রতিটি মানুষের মধ্যেই পশুশক্তি রয়েছে। পুরস্কার ও সাধন-ভজনের মাধ্যমে মানুষ যখন যথার্থ মনুষ্যত্বে উপনীত হয় তখন তার পশুভাব কেটে গিয়ে দেবভাব জাগ্রত হয়। আর তখনই সে প্রকৃত মরণাগত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে, সার্থক জীবনের অধিকারী হয়। দেবীর চরণতলে সিংহ সেই ভাবেরই প্রতীক।
দুর্গা দেবীর পদতলে দলিত অসুর। মহিষাসুর অসুর অর্থাৎ দেবদ্রোহী। তবে অসুর হলেও দেবী দুর্গার বরেই যেখানেই দেবী পূজিতা হবেন, সেখানেই তার চরণতলে স্থান পাবে মহিষাসুরও। তাই দেবীর পদতলে দলিত এই অসুর ‘সু’ এবং ‘কু’-র মধ্যকার চিরকালীন দ্বন্দ্বে অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক।
গণেশ সিদ্ধর দেবতা। পুরাণ অনুসারে, তিনি সবার আগে পূজিত হবেন। তার পূজা না করে অন্য কারো পূজা করার বিধান নেই। গণেশের আর এক নাম বিঘ্নেশ অর্থাৎ বিঘ্ননাশকারী। তিনি তারই প্রতীক। গণেশের বাহন ইঁদুর বা মূষিক। ইঁদুর মায়া ও অষ্টপাশ ছেদনের প্রতীক।
দুর্গা দেবীর ডানে অবস্থান লক্ষ্মী দেবীর। তিনি শ্রী, সমৃদ্ধি আর বিকাশের প্রতীক। কমল বা পদ্মের মতো সুন্দরী বলে তার রঙ কমলা। লক্ষ্মী দেবীর বাহন হচ্ছে পেঁচা। অবশ্য হিন্দু শাস্ত্রের কোথাও পেঁচাকে লক্ষ্মীর বাহনের মর্যাদা দেয়া হয়নি। এই বিশ্বাস একান্ত বাঙালির লোকবিশ্বাস বলেই অনেকে উল্লেখ করেছেন।
পুরাণ ও পুরাণোত্তর যুগে সরস্বতী বাক্য বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী বাগদেবীরূপে প্রসিদ্ধা। তাকে বিদ্যার দেবী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আধুনিককালে তার বাহন হচ্ছে হংস বা হাঁস। বেদ বা উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ ‘সূর্য’। একটি মত অনুসারে জানা যায়, হংস পরমাত্মার প্রতীক, হংসই তত্ত্বমসি জ্ঞান। অন্য আর একটি মতানুসারে, হংস যেমন প্রচুর আহার করে নির্যাসটুকু ধারণ করে বাকিটুকু মলাকারে ত্যাগ করে, তেমনি আহরিত জ্ঞানের ভালোটুকু গ্রহণ করে মন্দটুকু হংসবৎ ত্যাগের জন্য প্রতীকীভাবে হংসকে জ্ঞানবেদীর বাহন করা হয়েছে।
দুর্গার পুত্র হিসেবে কার্ত্তিক শারদীয় দুর্গাপুজোয় পূজিত হন। তিনি সৌন্দর্য আর শৌর্যবীর্যের প্রতীক। তার বাহন হচ্ছে শিখী। শিখা আছে যার সে-ই শিখী, অর্থাৎ আগুন। শিখী শব্দের অন্য অর্থ হলো ‘ময়ূর’। ময়ূরের দেহে যেমন আছে অনুপম সৌন্দর্য তেমনি রয়েছে তার কদাকার পদযুগল। স্বীয় রূপগুণে অহংকারী না হয়ে আপন কদাচারের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার শিক্ষা দেয় প্রতীকী ময়ূর।
এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সব সময় মনুষ্যত্বের প্রাণীকে দেবদেবীর বাহন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। যুগ এবং সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাহনেরও কিন্তু পরিবর্তন ঘটেছে। ছোট্ট দুটি উদাহরণ দেয়া যাক। বর্তমানে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা হলেও বিভিন্ন সময়ে তার বাহন ছিল ঘোড়া, হাতি, সিংহ, কচ্ছপ, হাঁস, ময়ূর ইত্যাদি। একসময়ে গরুও লক্ষ্মীর বাহন ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তার সব বাহনই হাতছাড়া হয়ে যায়। সিংহ চলে যায় দুর্গার দখলে, কার্ত্তিক নিয়ে নেন ময়ূর। হাঁস চলে গেল সরস্বতীর আয়ত্তে। শেষমেষ তিনি পেঁচাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার বাহন হতে রাজি করালেন। অন্যদিকে পুরাণতন্ত্রে হংসবাহনা সরস্বতীর উল্লেখ কম। মেষ, সিংহ এবং ময়ূর বাহনযুক্ত সরস্বতীর অনেক প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। পুরাণতন্ত্রের বৃহৎ বর্ণনায় সরস্বতী চতুর্ভুজা। বর্তমান সময়ের সরস্বতী প্রায় সব জায়গাতেই দ্বিভুজা, হাতে বীণা অপরিহার্য। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ের মতে, ‘দ্বিভুজা বীণাপানি সরস্বতী মূর্তি গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে’।
দুর্গাপূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি :
মূল সূচনা সাধারণত মহাষষ্ঠী থেকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কুলাচার অনুসারে ভাদ্রকৃষ্ণা নবমী বা মহালয়া থেকে এর সূচনা। আর সমাপ্তি হচ্ছে বিজয়া দশমী, তারিখ আশ্বিন শুক্লপক্ষ অথবা চৈত্র শুক্লপক্ষ উদযাপন প্রথানুসারে পনেরো, দশ বা পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানিকতা। সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক’দিনের একটি রবিবরণ জানা যাক।
ষষ্ঠী : বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস;
মহাসপ্তমী : নবপত্রিকা প্রবেশ ও স্থাপন, সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ, সপ্তমীবিহিত পূজা;
মহাষ্টমী : মহাষ্টম্যাদিকল্পারম্ভ, কেবল মহাষ্টমীকল্পারম্ভ, মহাষ্টমীবিহিত পূজা, বীরাষ্টমী ব্রত, মহাষ্টমী ব্রতোপবাস, কুমারী পূজা, মহাপূজা ও মহোৎসবযাত্রা, সন্ধিপূজা ও বলিদান;
মহানবমী : কেবল মহানবমীকল্পারম্ভ, মহানবমী ও বিহিত পূজা;
বিজয়া দশমী : বিজয়া দশমীবিহিত বিসর্জনাঙ্গ পূজা, বিজয়া দশমী কৃত্য ও কুলাচারানুসারে বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা।
কবে থেকে দুর্গাপূজার প্রচলন :
দুর্গাপূজা একটি প্রাচীন উৎসব; কিন্তু তা কতটা প্রাচীন সেটি নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। ইতিহাসবিদ রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন, ‘বাঙালি সভ্যতার ইতিহাস দুর্গোৎসবের সহিত জড়িত’। মহিষমর্দিনী দুর্গার সবচেয়ে প্রাচীন যে মূর্তিটি পাওয়া গেছে তা পঞ্চদশ শতকের। প্রাচীনকালে যে দুর্গাপূজা হতো তার প্রকৃতি এবং রূপ ছিল ভিন্ন। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে যে দুর্গাপূজা হয় বা প্রচলিত রয়েছে তা বলতে গেলে পুরোপুরি বঙ্গীয় ব্যাপার। একটু অন্যভাবে বলা যায়, প্রাচীন পদ্ধতিরই লৌকিকরূপ, যা বর্তমানে পরিণত হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসবে। এটি অকালবোধন নামেও পরিচিত, কারণ অতীতে দুর্গাপূজা হতো বসন্তকালে এবং ওটাই ছিল দেবীপূজার প্রশস্ত সময় কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম কর্তৃক অকালে, অর্থাৎ শরৎকালে দেবীর পূজা করার প্রসঙ্গ থেকেই শারদীয় দুর্গাপূজার প্রচলন হয়।
বাংলাদেশে দুর্গাকে অবলম্বন করে উৎসবের একটি পরম্পরা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত আশ্বিনের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধন হয়। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী- এই তিন দিন পূজা হয় এবং বিজয়া দশমীতে হয় বিসর্জন। উত্তর ভারতে এই দশমীর দিনে বর্ণাঢ্য মিছিল করে রাবণের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় এবং রামলীলা গীত হয়। বিজয়ার পরদিন থেকে পনের দিন ধরে চলে বিজয়ার কোলাকুলি।
দুর্গাপূজার ধারাবাহিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এটা বলা যায় যে, পুরো ব্যাপারটাই বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। কারণ এর বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অসংলগ্ন অঙ্গ দেখলে এটি স্পষ্ট যে, এক দেশে দুর্গাপূজার বিবিধ সংস্কৃতি প্রবর্তিত ও বর্ধিত হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আচারবিধি বিভিন্ন সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
তথ্য মতে এ কথা জানা যায় যে, আমাদের দেশে ষোড়শ শতকে (১৬০৬ সালে) প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ (মতান্তরে নদীয়া জেলার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়)। সেই সময়ে তিনি প্রায় ৮-৯ লাখ টাকা খরচ করে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করেছিলেন।
বিভিন্ন গ্রন্থে দুর্গাপূজার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। হয়তো কংসনারায়ণ বা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় থেকে তা জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই তথ্যের আলোকে বলা যায়, এই বাংলায় আদ্যশক্তি মা মহামায়া দেবী দুর্গার আরাধনা হাজার বছর পূরণ করেছে। দুর্গাপূজার প্রধান আকর্ষণ ছিল এর আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান। যেমন- ভোগ, থিয়েটার, সংকীর্তন, ঢপ, যাত্রা প্রভৃতি। গ্রামের প্রজাদের জন্য এসব ছিল উন্মুক্ত। ফলে, নিরানন্দ গ্রামে নিরক্ষর গ্রামবাসীরা দিন কয়েকের উত্তেজনার জন্য অপক্ষো করতেন।
তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কীভাবে দুর্গাপূজা পালিত হতো তার বৈচিত্র্যময় এবং বিস্তারিত বিবরণ খুব একটা পাওয়া যায় না। তবে কিছু সমসাময়িক পত্রপত্রিকা আর কারো কারো আত্মজীবনীতে এর সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গাপূজা জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব হিসেবে প্রথম পালিত হয় উনিশ শতকে কলকাতায়। এরপর থেকে আস্তে আস্তে এটি ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। দুর্গাপূজাকে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত করার নেপথ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছেন তৎকালীন জমিদাররা। তারপরও প্রচলনের পর থেকে বাংলাদেশে এই দুর্গাপূজা সর্বজনীন এবং সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হতে প্রায় ৩০০ বছর লেগেছিল।
অধ্যাপক যতীন সরকারের ভাষ্য মতে জানা যায়, ময়মনসিংহে মুক্তাগাছা ও গৌরীপুরের জমিদারদের দুর্গাপূজা ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনেক মাইল হেঁটে প্রজারা জমিদার বাড়িতে পূজা দেখতে যেতেন। পূজা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হতো যাত্রা, কবিগান, কীর্তন ইত্যাদি। মুক্তাগাছাতে বিজয়ার দিন হাতির মিছিল হতো। প্রজারা পূজার একদিন রাজবাড়ির পূজাম-পে প্রাণভরে খাওয়া-দাওয়া করে রাজাকে আশীর্বাদ করতেন।
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অস্থিবিশারদ ডা. শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য ‘মোছেনি তাহার চিহ্ন’ শিরোনামে এক স্মৃতিকথায় দুর্গাপুজোর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন- ‘নবমীর দিন পাঁঠাবলি হতো, ওইদিন জমিদার বাড়ির লোকেরা আসত। তাদের জন্য মাছ-মাংসের এলাহী ব্যবস্থা। অন্যান্য দিন মাছ থাকলেও মাংস থাকত না। প্রতি বছর যারা ঠাকুর গড়ে, তারাই আসত, ঠাকুর গড়ত। পুজোর ঘরেই পুজো হতো। বলির জন্য পাঁঠাও আসত। রামমালা ছাত্রাবাস থেকে বহু ছেলে আসত। নিবেদিতা বোর্ডিং থেকে মেয়েরা আসত। বুড়িমা, ঠাকুমারা মিলে আত্মীয়দের সবাই আসতেন। সে এক রাজকীয় কা-। তিন মন দুধের সন্দেশ তৈরি হতো। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে লোক খাবে, অতএব বিশাল আয়োজন। একটা দিন পুরো গ্রামকে নিমন্ত্রণ করা হতো, সবাই আসত।’
দুর্গাপূজার ব্যয় একেবারে কম ছিল না কোন কালেই। বেশ খরচ করেই এই উৎসব পালন করা হতো, বলা যায় এখনও তা হয়ে থাকে। ১৮৬১ সালের একটি হিসেবে দেখা যায়, প্রতিমা, সাজসজ্জা, বলি, লোক খাওয়ানো, বাদ্য, নৃত্যগীত এবং পুরোহিতের দক্ষিণাবাবদ খরচ প্রায় ২০০ থেকে ৪৯০ টাকার মতো। তৎকালীন টাকার হিসেবে ঐ পরিমাণ কম তো নয়ই বরং বেশিই বলা চলে। পরবর্তীকালে এই ব্যয় নির্বাহ করতে না পারার কারণেই কিন্তু পারিবারিক পূজা ধীরে ধীরে কমে আসে এবং বারোয়ারি বা ‘সর্বজনীন’ পূজার প্রচলন শুরু হয়। ব্যক্তি উদ্যোগে বা পারিবারিক উদ্যোগেও যে পূজা হচ্ছে না তা নয়, তবে পাকিস্তান আমল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে যত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার প্রায় বেশিরভাগই বারোয়ারি বা সর্বজনীন। ঢাকায় বাংলাদেশ স্বাধীনের পর থেকে জাতীয়ভাবে সর্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে।
উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে ঢাকায় দুর্গাপূজা পালনের অল্পবিস্তর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে জানা যায়, সেই আমলে এক বাড়িতে লাল দুর্গার প্রতিমা তৈরি করা হতো। সূত্রাপুরে ঢাকার বাবু নন্দলালের বাড়িতে দোতলার সমান উঁচু প্রতিমা বানানো হতো। অতীতে দুর্গাপূজার সময় ছাগল, মহিষ, শূকর, হরিণ, পাখি ইত্যাদি বলি দেয়া হতো। বর্তমানে অবশ্য বলির প্রচলন নেই বললেই চলে। একটি সময় ছিল যখন দুর্গাসহ অন্যান্য মূর্তির শরীরে সোনার গহনা পরানো হতো এবং তৎসহ প্রতিমা বিসর্জন দিত। এই পূজায় হিন্দুদের সকল বর্ণের লোকেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে। কোনরকম ভেদাভেদ এখানে গণ্য করা হয় না। সকল বর্ণ, গোত্র আর বিভিন্ন পেশার মানুষের মহামিলন ঘটে শারদীয় দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে। সারা বছরের দুঃখ, বেদনা, ক্লেশ ভুলে মহামিলনের আনন্দে মেতে ওঠে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষ। সারা বছরের দুঃখ, বেদনা, ক্লেশ ভুলে মহামিলনের আনন্দে মেতে ওঠে দেশের হিন্দু সমপ্রদায়। তাদের আনন্দছটায় আলোকিত হয়ে ওঠে দেশের প্রতিটি পূজামণ্ডপ।
আসছে বছর আবার হবে :
খড়ের উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে প্রকৃতির যে প্রতিমা শিল্পী তৈরি করেন তা অপার্থিব কিছু নয়। মানবী যেমন অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা, দেবী দুর্গাও তাই। দেবীর রূপ ও রূপান্তরকে প্রভাবিত করেছে কিছু লৌকিক সংস্কার ও ভাবনা। মাটির ভেতর আছে খড়, যা ধানের কথা মনে করিয়ে দেয়। ধান মানেই ধন। মাটিকে কর্ষণ করে ধান ফলায় সাধারণ মানুষ। তাই এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ঘরেই আশ্রয় পেয়েছেন দেবী।
নারীরূপী প্রকৃতিকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করে আত্যন্তিক সুখ অনুভব করে সনাতন ধর্মীরা। মা শব্দের সঙ্গে জড়িত সন্তানের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনার অনিশেষ অনুভূতি। আর তাই শুধু বাঙালির দুর্গা বাঙালি সংস্কৃতিরই নিজস্ব সৃষ্টি। বাংলার মাটিতে তিনি শক্তিরূপিণী হয়েও একাধারে বাঙালি হিন্দুর কন্যা ও জননী। প্রকৃতির রূপকল্পনায় শিল্পী দুর্গাকে দশহস্তারূপে এঁকেছেন। এই দশ হাত হচ্ছে দশটি দিক থেকে সন্তানকে রক্ষার চেষ্টায় অনুক্ষণ ব্যাপৃত।
সবকিছু মিলিয়েই শারদীয়া দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। বহু প্রাচীনকাল থেকেই দুর্গাদেবী তার একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করে আছেন বাঙালির মন, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর নানাবিধ চারু ও কারুকলায়। দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের যে আবেগ এবং তার যে দারুণ বহিঃপ্রকাশ, তার অসাধারণ প্রমাণ মেলে এই কয়েক দিনের আনন্দ উৎসবে।
লেখকের কথা: রানা চক্রবর্তী
রানা চক্রবর্তী পেশায় সরকারী কর্মচারী। নেশা ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা আর লেখালিখি। নিজেকে ইতিহাসের ফেরিওয়ালা বলতে ভালবাসেন।
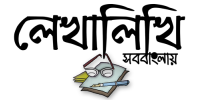


নতুন কিছু জানলাম..
দেবী দূর্গার আগমন এবং গমনের সমস্ত বহনের বিস্তারিত নিয়ে যদি কিছু লেখেন খুব উপকৃত হব। এবং ধন্যবাদ এই লেখাটির লক্ষ্মী এবং সরস্বতী সম্পর্কে অজানা তথ্য আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে।