লেখক : অভীক সিংহ
ট্রেনটা স্টেশনে ঢুকছে। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে সিট থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নাকে ভেসে আসল সেই পুরনো চেনা গন্ধটা – কংসাবতী নদীর পলিমাটির গন্ধ। আজ প্রায় কুড়ি বছর পরে পুজোর সময় আসতে পেরেছি নিজের ফেলে আসা শহর মেদিনীপুরে। আমার ছোটবেলার সব দুষ্টুমি, কৈশোরের অ্যাডভেঞ্চার, তারুণ্যের প্রেম – সব গায়ে মেখে আদিম নিস্তব্ধতায় ইতিহাসের সাক্ষ্য বয়ে চলেছে এই শহরটা। ট্রেনটা থামতেই নেমে পড়লাম স্টেশনে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম – নাহ, শেষ যেমনটা দেখে গিয়েছিলাম, তার সাথে বিস্তর ফারাক। অনিবার্য বিবর্তন যেন নিজের থাবা বসিয়েছে অতীতের জলছবিতে, তাই চেনা রঙগুলো যেন বর্তমানের চক্রব্যূহে দাঁড়িয়ে থাকা অতীতের “আমি”র দিকে তাকিয়ে হাসছে এক ব্যঙ্গের হাসি। সময়ের তো এটাই নিয়ম – এই ভাবতে ভাবতেই স্টেশনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে তাকালাম রিক্সাস্ট্যাণ্ডের দিকে। এই স্ট্যাণ্ডের ঠিক পাশেই খোকনদার ছোট্ট চায়ের দোকানটা ছিল ফি বিকেলে আমাদের আড্ডা আর গুলতানির ঠেক। চা, বিস্কুট, সিগারেট হাতে দেশ-রাজনীতি নিয়ে অগ্নিগর্ভ আলোচনা করতে করতে স্বপ্ন দেখতাম নিজেদের পারিপার্শ্বিককে সমূলে বদলে দেওয়ার। কিন্তু সেই পারিপার্শ্বিকের সাথে ক্রমবর্ধমান বয়সের গোপন শলা যে কখন আমাদেরকেই ভিতর থেকে একটু একটু করে বদলে দিয়েছে, সেটা বোধগম্যই হয়নি। খোকনদাও হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির গভীরে, সেই চায়ের দোকানটার স্থান নিয়েছে একটি অত্যাধুনিক গিফট শপ, আর রিক্সাকে ঠেলে সরিয়ে তার জায়গা নিয়েছে টোটো। আমার চেনা স্মৃতিগুলোর সাথে বারবার মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। নাহ, পারছি না। বুঝতে পারছিলাম, শহরের বহিরঙ্গে নবীনত্বের প্রতিফলন হয়ত আমার ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীনত্বেই।
দেবরাজ বলেছিল সোজা ওর বাড়িতে চলে আসতে, ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিল। টোটোওয়ালাকে বললেই নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আজ এতদিন পরে নিজের ফেলে আসা ঠিকানার খোঁজে একবার যাব না? একবার দেখে আসব না, অতীতের আঁধারিত তুলসীতলায় স্মৃতির টিমিটিমে প্রদীপটা আজও কেউ জ্বালিয়ে রেখেছে কি না? তাই আবার হয় নাকি? দেবরাজকে ফোন করে বলে দিলাম যে আমার আসতে একটু সময় লাগবে। বলে ফোনটা পকেটে রেখে একটা টোটোতে চেপে বসলাম, “রবীন্দ্রনগরের দিকে চলো।”
“রবীন্দ্রনগরে কোথায় যাবেন?” টোটোওয়ালা জিজ্ঞাসা করল।
“তুমি সব পেয়েছির আসরের মাঠটার দিকে চলো।”
কথা শেষ হতেই টোটো এগোল। আস্তে আস্তে স্টেশনের বাইরের ভিড় পিছনে রেখে টোটো এগোল বড় রাস্তার দিকে। চার্চের মোড়, কেরাণিটোলা, বার্জটাউন পেরিয়ে টোটো এগিয়ে চলেছে, আমার চোখ রাস্তার দিকে। ছেলেবেলার অধিকাংশ স্মৃতিই ঢেকে গিয়েছে বিকশিত কংক্রীটের জঙ্গলের আড়ালে। সকালে কচুরি আর সিঙাড়ার সুবাস ছড়িয়ে দেওয়া মিষ্টির দোকানটা, চাচা চৌধুরি আর অরণ্যদেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছোট্ট বইয়ের দোকানটা, নতুন ক্যাম্বিস বলের ছোঁয়ার স্বাদ এনে দেওয়া খেলার দোকানটা, আমাদের ঝাঁপিতে ক্রিকেটারদের কার্ডের সম্ভারের গুপ্তধনের সন্ধান দেওয়া চকলেটের দোকানটা – অনেক খুঁজেও তাদের কোথাও দেখতে পেলাম না। “আমার ঠিকানাটা আগের মত আছে তো?” প্রশ্নটা মনের মধ্যে একবার গুমরে উঠল। ভাবতে ভাবতেই একটা বাঁক নিয়ে টোটো ঢুকল রবীন্দ্রনগরের রাস্তায়। বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য উত্তেজনা জেগে উঠল। “আমার বাড়ি” – কথাটা যেন নিজের মনে মনেই একবার বলে উঠলাম। দেখতে দেখতে টোটো এসে থামল ‘সব পেয়েছির আসর’ মাঠটার সামনে। এই মাঠটার পিছনে একটা বাড়িতেই কাটিয়েছি প্রায় চব্বিশটা বছর – ছোট থেকে বড় হওয়া, বোনের জন্ম। টোটো থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম সেদিকে। বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম, হাত রাখলাম বাইরে ছোট দরজাটার উপরে। কে বলে, টাইম মেশিন বলে কিছু হয় না? স্মৃতি যেন একধাক্কায় নিজের ভাণ্ডার উজাড় করে দিল আমার সামনে, এক লহমায় নিজের ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার প্রত্যেকটা দৃশ্য যেন একটা ফ্ল্যাশব্যাকের মত ভেসে উঠতে লাগল। নিজের অজান্তেই কখন যেন নাকটা জ্বালা করে উঠল, ভিজে আসতে লাগল চোখের কোণটা। ওইভাবেই দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় বাড়ির দরজাটা খুলে গেল, বাইরে বেরিয়ে আসলেন একজন ভদ্রলোক। “কাউকে খুঁজছেন?” আমি চোখটা মুছে নীরবে মাথা নেড়ে “না” বলে ওখান থেকে সরে আসলাম। সময়ের সাথে বদলে যায় পরিচয়, বদলে যায় ঠিকানাও। নতুন ভাড়াটে এসেছে আমার পুরনো ঠিকানায়, আর আমি আজও নতুন ঠিকানার সন্ধানে। বাড়িটা থেকে সরে এসে এগোলাম মাঠটার দিকে। সে কিন্তু এখনও একই আছে। মাঠে প্যাণ্ডেল তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, পুজোর তো আর মাত্র কয়েকদিনই বাকি। আর তার সামনে ক্রিকেট খেলছে কিছু কচিকাঁচার দল। আমি মাঠের ধারে একটা বেঞ্চের উপরে ব্যাগটা পাশে রেখে বসলাম, আনমনে দেখতে লাগলাম ওদের ক্রিকেট খেলার দিকে। খেলতে খেলতে একটা উঁচু ছক্কা গিয়ে পড়ল মাঠের সামনের বাড়িটার উঠোনে। একজন ছুটল বলটা ফেরত আনতে। আমি তাকিয়ে দেখলাম বাড়িটার দিকে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বাড়িটা, উঠোন, ঠাকুমা, দাদু, ক্রিকেটের বল, পায়েস, মৃত্যু – বেয়াদপ স্মৃতি আবার আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল সেই হারিয়ে যাওয়া গল্পটার সামনে। চোখের সামনে এক এক করে ভেসে উঠতে লাগল মনে গহীনে হারিয়ে যাওয়া সেই দৃশ্যগুলো।
যতদূর মনে পড়ে, তখন আমার ক্লাস সিক্স। রোজ নিয়ম করে স্কুল থেকে ফিরে এসে খেয়ে দেয়েই ব্যাটটি বগলদাবা করে ছুটতাম মাঠে। তখন টিভির স্ক্রীণ এবং আমাদের মাথাজুড়ে রাজত্ব করছে সচিন-আজহার-শ্রীনাথ-কুম্বলে। আর সেই রাজায়-রাজায় যুদ্ধের প্রাত্যহিক মহড়া চলত খেলার মাঠে, আর পাড়া-প্রতিবেশীদের জানালার কাচগুলো উলুখাগড়ার ভূমিকা পালন করত। তো মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত উত্তেজনার বশে বলটা আকস্মিক মিসাইল অবতার নিয়ে ভূমিষ্ঠ হত মাঠের ঠিক সামনের বাড়িটার উঠোনে। বাউণ্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করার দরুণ আমার কপালেই জুটত সবচেয়ে আপত্তিজনক কাজটা – বলকে ছলপূর্বক শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি নিয়ে আসা। আমি গিয়ে সেই বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার কয়েক সেকেণ্ড পরেই দরজাটা খুলে যেত, আর বলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসতেন তিনি, যাঁকে ঘিরেই এই স্মৃতি – পাড়ার সবার প্রিয় “ঠাকুমা”। বয়স আন্দাজ তিরাশি বছর, দুধে-আলতা গায়ের রঙ, মাথায় বিশাল বড় খোঁপা, মাথার বড় করে সিঁদুরের টিপ, সিঁথির মাঝখানে চওড়া সিঁদুর, পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি, আর মুখশ্রী সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রতিমার মত। কিন্তু স্বভাববশত ঠাকুমা ছিলেন খুবই গম্ভীর, এবং ওনার প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে কচিকাঁচারা তো কোন ছাড়, পাড়ার বড়রাও বিশেষ কিছু বলতে পারত না। তাই ওনাকে সামনে দেখলেই একটা অত্যাশ্চর্য শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে আমার গলার আওয়াজ গলার ভিতরেই রয়ে যেত। ঠাকুমা বাইরে বেরিয়ে এসে খুব গম্ভীরভাবে “এবারে ফেরত দিচ্ছি, আর যেন না পড়ে” বলে বলটা আমার হাতে দিয়ে আবার ভিতরে চলে যেতেন, আর আমি এক বিস্ময়চকিত গুণমুগ্ধ ভক্তের মত চেয়ে থাকতাম ওনার দিকে। রোজ ভোরবেলায় ঠাকুমাকে দেখতাম পাড়ার বিভিন্ন গাছ থেকে ফুল তুলে সাজিতে ভরে নিজের বাড়ির দিকে এগোতেন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোনকালেই এর অন্যথা হয়নি। উনি বলতেন, “সকাল সকাল স্নান করে ভাল ফুল নিয়ে পুজো দিয়ে দেখিস, সব ভাল হবে।” হয়ত এইরকম সরল এবং অটল ঈশ্বরবিশ্বাসের জন্যই প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় পুজোর জোগাড়ের দায়িত্ব থাকত ঠাকুমার উপরেই। তাঁরই সনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে পাড়ার সব কাকিমা-জ্যেঠিমারা পুজোর যাবতীয় জোগাড়যন্ত্র করতেন, একচুল এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। তাই ঠাকুমা হয়ে উঠেছিলেন আমাদের পাড়ার পুজোর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর স্বভাবে গম্ভীর হ’লে কী হবে, ঠাকুমার নজর থাকত সবার দিকে। কার জ্বর হয়েছে, কার শরীর খারাপ, কার বাড়িতে রান্না হয়নি – কোন এক যাদুমন্ত্রবলে ঠাকুমার কাছে পৌঁছে যেত সব খবর। পুরো পাড়াটাই যেন তাঁর স্নেহঘন আঁচলের নিচে পরমাদৃত সন্তানের মত। একবার আমার বাড়াবাড়ি রকমের জণ্ডিস হয়ে বেশ কয়েকদিনের জন্য শয্যাশায়ী হলাম। রোগগ্রস্ত অবস্থায় একদিন ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি, এমন সময় জানালার দিক থেকে একটা গম্ভীর, কিন্তু স্নেহমাখা আওয়াজ ভেসে আসল, “কী রে, তাড়াতাড়ি ওঠ, উঠোনে বল ফেলতে হবে তো।” তাকিয়ে দেখি, জানালায় ঠাকুমা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে, হাতে ফুলের সাজি। আমাকে তাকাতে দেখে হাত নেড়ে আশ্বাস দিলেন, “তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবি রে।” জণ্ডিসের ক্লান্তির বশে মস্তিষ্কের অর্থহীন নীরব প্রগলভতায় সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, কোন দৈবশক্তি এসে যেন আমাকে খুব কাছ থেকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গেল। আশ্চর্যভাবে সে যাত্রায় খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছিলাম।
এইভাবেই সময় তার নিজস্ব গতিবেগেই এগিয়ে চলছিল। একদিন বিকেলে পুরোদমে আমাদের ক্রিকেট ম্যাচ চলছে, খেলা গড়িয়ে এসেছে প্রায় শেষ পর্যায়ে। জিততে গেলে বিপক্ষ দলের দরকার পাঁচ বলে আর আঠার রান, টানটান উত্তেজনার মুহূর্ত। ঠিক এই সময় দারা সিংয়ের মত শক্তিধর ব্যাটসম্যান কত্থকের ভঙ্গিমায় ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে সপাটে মারল একটা ছক্কা, আর বাউণ্ডারি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা “আমি”-র বলাতঙ্ক সত্যি করে দিয়ে উড়ন্ত বলটা গিয়ে আশ্রয় নিল অকুস্থলে – ঠাকুমার বাড়ির উঠোনে। সমূহ বিপদ! কারণ গত পরশু আমারই মারা একটি ছক্কার বদান্যতায় ঠাকুমার বারান্দায় রাখা তাঁর শখের ফুলদানিটি পরলোকগত হয়েছে। সেই ফুলদানির শক এবং শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার আজ ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দুরুদুরু বুকে, কম্পমান ত্রস্তপদে এগিয়ে গেলাম ঠাকুমার বাড়ির দিকে। দরজায় কড়া নাড়তে একটু পরে বেরিয়ে এলেন ঠাকুমা, মুখ গম্ভীর। আমি কাঁপাকাঁপা গলায় বল ফেরত চাইতেই তিনি নির্ঘোষে আদেশ দিলেন, “যা, মাঠের সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।” আমি শুকনো মুখে গুটিগুটি পায়ে মাঠে গিয়ে সবাইকে কাছে ডেকে বললাম, “চল, ঠাকুমা ডাকছে। আজ কপালে দুঃখ আছে মনে হচ্ছে রে।” সবাই ব্যাট-বল মাঠে রেখে কিছুটা ভয়ে ভয়েই এগোলাম ঠাকুমার বাড়ির দিকে। পৌঁছে দেখি ঠাকুমা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার সামনেই। গম্ভীর স্বরে বাড়ির ভিতরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, “সবাই ভিতরে যা, হাতমুখ ধুয়ে উঠোনে গিয়ে বোস।” আমরা একটু অবাক হয়েই একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে কোন কথা না বলে সোজা বাড়ির ভিতর গিয়ে ঢুকলাম। এই প্রথমবার ঠাকুমার বাড়িতে পদার্পণ করলাম আমরা। ঢুকতেই প্রথম চোখে পড়ল ঠাকুমার ফুলের বাগান। উঠোনের দু’পাশে হরেক রকম ফুলের গাছ, তরিতরকারির গাছ, একটা লেবুগাছের ঝাড়, আরও কত কী। উঠোনের ঠিক মাঝখানে একটা তুলসীতলা, সেটার গায়ে সুন্দর করে আঁকা আলপনা। পাশে কল থেকে জল নিয়ে আমরা চটজলদি হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই ঠাকুমা উঠোনে মাদুর আর শতরঞ্চি বিছিয়ে আমাদের বসতে বললেন। আমরা সবাই বিনাবাক্যব্যয়ে বসে পড়তেই ঠাকুমা “তোরা একটু বোস, আমি আসছি” বলেই ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হ’লেন। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে আসলেন একটা বড় রেকাবিতে অনেকগুলো পায়েসভরা বাটি নিয়ে। আমাদের সবাইকে একটা করে বাটি দিয়ে বললেন, “খেয়ে দেখ তো কেমন হয়েছে?” আমি প্রথম চামচটা তুলে মুখে দিতেই – আহা, স্বর্গীয় পরমান্ন। আমি জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, “ঠাকুমা, আজ বাড়িতে কি কোন পুজো আছে?”
“কেন রে হতভাগা? পুজো না থাকলে বুঝি খাওয়াতে নেই?” ঠাকুমা কপট রাগের সাথে হাসিমুখে বললেন।
“তাহলে ঠাকুমা?”
“ওরে, আজ এই মুখপুড়ির সাথে আমার খুঁটি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল রে। বুঝলি?” বলতে বলতে ভিতরের ঘর থেকে দাদু বেরিয়ে আসলেন। দাদু মানে একেবারে সত্যিকারের দাদু – থুত্থুড়ে বুড়ো, শ্মশ্রুগুম্ফহীন চেহারা, মাথায় টাক, হাতে লাঠি, চোখে চশমা। দাদুকে দেখেই ঠাকুমা মাথায় আঁচল দিলেন, আর বললেন, “তোমার কি মুখে কিছুই আটকায় না? এই বাচ্চাগুলোর সামনে…”
“আরে এই বয়েসে তো তুমি আমার বউ হয়ে গিয়েছিলে, লজ্জা কিসের?”
দাদুর আশকারা পেয়ে আমাদের মধ্যে থেকে ডাম্পিদা বলে উঠল, “তাহলে দাদু, তোমাদের তো একেবারে সপ্তপদী কেস!”
“সপ্তপদী নয় রে হতভাগা,” দাদু শুধরে দিল, “বল, বালিকাবধূ কেস।”
দাদুর কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম। ঠাকুমা দাদুর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় বলে উঠলেন, “যাঃ, তুমিও না…”
তারপরে কেটে গিয়েছে আরও কয়েকটা মাস। দেখতে দেখতে এসে গিয়েছে মহালয়ার সকাল। অন্যান্য দিনের মতই উঠেছিল সূর্য, পাখিরাও ডেকেছিল অন্য দিনগুলোর মতই, আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘও জমেছিল প্রতিবছর আশ্বিনের শারদপ্রাতের মতই। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে “জাগো, তুমি জাগো” পুরো পাড়াকে জাগিয়ে তুললেও ঘুম ভাঙল না শুধু একজনের – আমাদের দাদু। মহালয়ার ভোরেই সবার আড়ালে মাতৃলোকে পাড়ি জমালেন তিনি। পিছনে রয়ে গেল তাঁর দুই ছেলে, এক মেয়ে, চারটি নাতি-নাতনি, এবং… ঠাকুমা। পাড়ার সব বড়রা যোগদান করল দাদুর শেষযাত্রায়। ছোটদের যাওয়া বারণ ছিল বলে আমরা জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখলাম দাদুর আস্তে আস্তে দূরে চলে যাওয়া। আর দেখলাম, ঠাকুমাকে বাড়ির দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে – যেন দাদুর সেই যাত্রার অন্তিম সাক্ষী। সেদিন হয়ত ঠাকুমার বাগানে ফুলগুলো পরিচর্যা পায়নি, তুলসীতলা পায়নি প্রদীপ, আর দরজার বাইরে বসে থাকা বেড়ালটা তার জন্য বরাদ্দ মাছের টুকরোটা। সূর্য ডুবে গেল।
তৃতীয়ার দিন বিকেলবেলা। মাঠে প্যাণ্ডেলের কাজ প্রায় শেষ। মাঠের অন্যদিকটায় আমরা ক্রিকেট খেলছি। হঠাৎই একটা জোরদার একটা শটে বলটা গিয়ে পড়ল ঠাকুমার বাড়িতে। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, কারও এগিয়ে যেতে সাহস হচ্ছে না। শেষে উপায়ান্তর না দেখে আমিই একটু সাহস যুগিয়ে এগিয়ে গেলাম ঠাকুমার বাড়ির দিকে। দরজায় কড়া নাড়ার কয়েক মুহূর্ত পরেই খুলে গেল দরজাটা। ঠাকুমা বেরিয়ে এলেন। ইনি কে? ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাতেই যেন আমার পিঠের মধ্যে দিয়ে নেমে গেল একটা হিমেল স্রোত, আর গলার মাঝে দলা পাকিয়ে উঠল একটা ভীষণ বোবাকান্না। ঠাকুমার কপালে সেই ভোরের সূর্যের মত ঊজ্জ্বল সিঁদুরের টিপ নেই, অবিন্যস্ত চুল যেন পিপাসাগ্রস্ত, পরনে আলুথালু সাদা থান, মুখে যেন এক অদৃশ্য কালির ছাপ, আর দু’চোখে এক উদভ্রান্ত দৃষ্টি – যেন কাউকে দিগভ্রষ্টের মত ব্যর্থ সন্ধান করে চলেছে। তিনি আমার দিকে বলটা এগিয়ে দিলেন, কিন্তু আমি এক পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতই হয়ে পড়েছি সর্বশক্তিরহিত। চেষ্টা করেও তুলতে পারলাম না আমার হাতটা। ঠাকুমা হয়ত আমার অবস্থা কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেই আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমার হাতে বলটা তুলে দিলেন। ওনার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি, যে হাসিতে মনের কোণে জমে থাকা সকল বেদনা উৎসারিত হয়ে, হৃদয়ের ক্ষত বেয়ে গড়িয়ে পড়া একবিন্দু রুধিরধারা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মুখে। তাঁর সেই বেদনার্ত হাসিতেই তিনি যেন অচিরেই মিথ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছিলেন তাঁর জীবনের সব হিসাব নিকাশের অঙ্কগুলোকে। একাকীত্বের জ্বালায় তাঁর ভস্মীভূত সত্তা যেন ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়ে চলেছিল জাগতিক দৈনন্দিনতার ঊর্ধ্বে। কোন রাগ নেই, কোন গাম্ভীর্য নেই, শুধু মনের শূন্য ভাঁড়ারে সযত্নে গোপন করে রাখা আঁধারিত কুলুঙ্গির তাক থেকে পেড়ে আনা শেষ সঞ্চিত অনুভূতি দিয়ে এক আকাশ ভালবাসা আর স্নেহসিক্ত স্বরে বললেন, “ভাল থাকিস রে বাবা।” বলেই তিনি ভিতরে চলে গেলেন, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমিও হয়ত ঠাকুমার সামনে উপুড় করে দিতে চেয়েছিলাম এক অন্তরীক্ষ অনুভূতি। কিন্তু পারলাম না। কম্পমান ঠোঁট আর নীরব চোখের জল বাদ সাধল। একটা অসহনীয় যন্ত্রণা যেন ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল অন্তরাত্মাকে। “হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ’ল…” ঠাকুমার গলা ভেসে আসছিল বাড়ির ভিতর থেকে। মনের গভীর থেকে একটা আশঙ্কামিশ্রিত আকুতি ঠেলে উঠে আসল, “ঠাকুমা, তোমায় আবার দেখতে পাব তো?”
না, আর কোনদিনও পাইনি। একাকীত্বের বেদনা আর বাঁচতে দেয়নি আমাদের ঠাকুমাকে। অষ্টমীর রাতে সন্ধিপুজোর সময় তিনিও পাড়ি জমালেন মাতৃলোকে। বাবার কাছে সেদিন শুনেছিলাম, বিয়ের সময় দাদুর বয়স ছিল দশ আর ঠাকুমার চার, এবং মারা যাওয়ার সময় ঠাকুমার চুরাশি এবং দাদুর নব্বই। দীর্ঘ আট দশকের সাহচর্য, খুনসুটি, ঝগড়া, বন্ধুত্ব, প্রেম এবং ভালবাসার মানুষটির অকস্মাৎ প্রয়াণ ঠাকুমা সহ্য করতে পারেননি। তাই দাদু চলে যাওয়ার মাত্র আটদিনের মাথাতেই ঠাকুমাও পিছু নিলেন। জীবনের জ্ঞান হওয়ার আগেই যার হাত ধরে জীবনের পথচলা শুরু, জীবন পথের শেষে ঠাকুমা দিগভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত খুঁজে চলেছিলেন তারই হাত। বালিকাবধূ হয়ে সপ্তপদ অতিক্রম করে যে বন্ধন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, তা হয়ত ছিল জীবন-মৃত্যুর অতীত।
“এবারে বল ফেললে ঠ্যাং ভেঙে দেব।”
হঠাৎ চিৎকারে চিন্তার সূত্রটা কেটে গেল। ঠাকুমার বাড়ি থেকে চিৎকারটা ভেসে আসল। ঠাকুমার ছেলেমেয়েরা বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে, অজানা মানুষ তার অজানা গল্প নিয়ে সেখানে পেতেছে চেনা সংসার। সময়ের সাথে পুরনো ঠিকানায় বাসা বাঁধে নতুন পরিচয়। কিন্তু নিছক ভালবাসা কি পরিবর্তনশীল ঠিকানার তোয়াক্কা করে? হয়ত করে না। আজ এই বাড়িটায় ঠাকুমা নেই, দাদুও নেই, তাঁদের পরিবারও নেই। তাঁদের ঠিকানা সময়ের সাথে মুছে গিয়েছে, মুছে গিয়েছে পরিচয়ও। কিন্তু তাঁদের ভালবাসা সুদূর নক্ষত্রমাঝে পেয়ে গিয়েছে অমরত্বের ঠিকানার সন্ধান। আর কী চাই? আমি নীরবে একবার আকাশের দিকে চেয়ে হাসলাম। তারপরে পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেবরাজকে কল করলাম, “গুরু, আমি আসছি।”
“হ্যাঁ, চলে আয়। ঠিকানাটা মনে আছে তো?”
আমি মনে মনে হাসলাম। বললাম, “আছে রে, আসছি।”
মাঠ থেকে বেরিয়ে একটা টোটোতে উঠে পড়লাম। সাথে নিয়ে চললাম আমার শহরের একটা না-বলা গল্প, পিছনে পড়ে রইল চেনা ঠিকানা, বাড়ি, পরিচয়…
লেখক পরিচিতি : অভীক সিংহ
গল্পটির লেখক ডঃ অভীক সিংহের জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। পেশায় অর্থনীতির অধ্যাপক এবং গবেষক। তবে ভালবাসাটা আজও লেখালিখি, পেন্সিল স্কেচ, যন্ত্রসংগীত, এবং নিত্যনতুন রান্নাবান্নার সাথেই রয়ে গিয়েছে। প্রথম বই "R.E.CALL: এক Recollian-এর গল্প" প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে। দাদুর হাত ধরে কবিতা দিয়ে লেখালিখির সূত্রপাত হলেও এখন প্রবন্ধ এবং গল্পতেই মনোনিবেশ করেছেন।
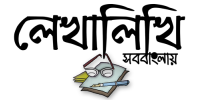


চমৎকার লেখা!
অনেক ধন্যবাদ গুরু ❤️❤️
খুব ভালো লাগলো।
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কাকিমা ❤️❤️