লেখক: ঋক ঋকমন্ত্র
শান্তিদার ভালো নাম যে কী, তা পাড়ার অনেকেই জানতো না। কিন্তু সবাই শান্তিদাকে ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। কারণ, কলোনীর কেউ কোনোদিন শান্তিদাকে কোনো কুকথা বলতে শোনেনি, কোনো অশান্তিতে জড়াতে দেখেনি।
এহেন শান্তিদার একটা হোটেল ছিল বড় রাস্তার ধারে। ফুটপাথ দখল করে ভাতের হোটেলটা শান্তিদা তৈরি করেছিলেন একাত্তর সাল নাগাদ। পাক হানাদার বাহিনীর তাড়া খেয়ে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে এপার বাংলায় পালিয়ে আসার পর শান্তিদাকে তাঁর পরিবারের পেট চালাবার জন্যে কিছু একটা করতেই হতো। বাংলাদেশেও শান্তিদার বাবার একটা ছোটখাটো হোটেল ছিল। তাই এপারে এসেও শান্তিদা সেই ধারা বজায় রেখে হোটেল খুলে ফেলেছিলেন।
প্রথম দিকে যথারীতি অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল শান্তিদা আর তার ভাই গোপলকে। সে যতই একরত্তি হোটেল হোক, ব্যবসা করতে গেলে তো পুঁজি লাগে। তাই চড়া সুদে মোটা টাকা কর্য করে ভাইয়ের সাথে শান্তিদা নেমে পড়েছিলেন ব্যবসায়, শখ করে দোকানের নাম রেখেছিলেন ‘শান্তিদার হিন্দু হোটেল’।
দিনের বেলা ব্যবসা সামলাতো গোপাল আর সন্ধ্যে থেকে সেই রাত বারোটা পর্যন্ত বসতেন শান্তিদা। এলাকাতে যেহেতু বেশ কয়েকটা মেসবাড়ি ছিল, তাই শান্তিদার খদ্দেরের অভাব হতো না। তাছাড়া পথচলতি কিছু লোকজন তো খেতে আসতোই।
বাংলাদেশ থেকে কপর্দক শূন্য অবস্থায় আসা শান্তিদার সংসারে হোটেল চালিয়ে বেশ টাকা আসতে লাগলো। পরিবার স্বচ্ছল হলো। পাশের পাড়ায় তিন কাঠা জমি কিনে বাড়ি করলেন শান্তিদা। ভাইয়ের বিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।
কিন্তু কথায় বলে, সুখ কারোর জীবনেই চিরস্থায়ী হয় না। শান্তিদার ক্ষেত্রে প্রবাদটা অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেলো। গোপাল বিয়ে হতেই বেগরবাই শুরু করলো। ব্যবসা থেকে আসা টাকার একটা মোটা অংশ মাসোহারা হিসেবে দাবি করে বসলো। শান্তিদা বুঝলেন, নতুন বউ নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছে। এমনিতেও শান্তিদা কখনো গোপলকে কষ্টে থাকতে দেননি। মাসে-মাসে হাত খরচ দিতেন। কিন্তু গোপাল সোজা পথে চলার বান্দা ছিলো না। সে জোরদার ঝগড়াঝাটি শুরু করলো। শান্তিদা তাকে বাবা-বাছা করে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন। শান্তিদার বউ লতাও তার ঠাকুরপোটিকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু শেষমেস একটা মোটা অংকের টাকা আদায় করে বউ নিয়ে বাড়ি ছাড়লো গোপাল। রেললাইনের ওপারে বাড়ি ভাড়া নিলো আর স্টেশনের কাছেই শ্বশুরের পয়সায় একটা ছোট মুদির দোকান খুললো।
ভাইকে হারিয়ে বুকে বড় ব্যথা পেলেন শান্তিদা। বাবা-মা চোখ বোজার পর গোপালকে তিনিই বড় করে ছিলেন। ভাই যে এইভাবে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে – সেটা শান্তিদা কোনোদিনও ভাবেননি।
সে যাই হোক, শান্তিদা মুখ বুজে সব যন্ত্রণা সহ্য করে আবার ব্যবসায় মন দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মনটা তাঁর মরে গেলো। কেউ আর শান্তিদার আগের সেই সদা হাস্যময় রূপটাকে দেখতে পেল না। যে লোকটা রোজ সকালে নিজে ঘুরে-ঘুরে হোটেলের জন্যে একগাদা বাজার করতো, যে লোকটা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভালো-মন্দ সব রান্নার তদারকি করতো, যে লোকটা সব সময় তার সব খদ্দেরের সাথে হাসিমুখে কথা বলতো, সেই লোকটা কেমন যেন বদলে গেল। প্রায় রোজই হোটেলের রেডিওতে গান শুনে খেতে-খেতে অনেকেই চেষ্টা করতো শান্তিদার মনের কথা জানার। কিন্তু শান্তিদা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। যেন কারোর কোনো কথাই শুনতে পেতেন না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে শূন্য দৃষ্টিতে দূরে তাকিয়ে থাকতেন।
গোপাল বউ নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার ঠিক তিন বছর পর এক দুপুরে হোটেলে বসেই খবরটা পেলেন শান্তিদা। পাড়ারই বখাটে ছেলে অপু দৌড়তে-দৌড়তে এসে জানালো, ‘দাদা! রান্না করতে গিয়ে বৌদি পুড়ে গেছে!’
পাগলের মতো দৌড়ে বাড়ি পৌঁছলেন শান্তিদা। সেখানে তখন পাড়া-প্রতিবেশীর ভিড়। ক্লাবের ছেলেরা ততক্ষণে আগুন নিভিয়ে ফেলেছে। কিন্তু লতার অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার শরীরের নব্বই শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। তাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেও কোনই লাভ হলো না। ডাক্তারদের সব চেষ্টায় জল ঢেলে লতা এক সপ্তাহ পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।
এত বছর ধরে যে হোটেল কোনদিনও এক বেলার জন্যেও বন্ধ থাকেনি, লতার মৃত্যুতে সেই শান্তিদার হিন্দু হোটেলের ঝাঁপ বন্ধ ছিল টানা এক মাস। শান্তিদা বাড়ি থেকে সেই একমাস বেরোননি, কারোর সাথে কথা বলেননি, দাড়ি কামাননি, খাওয়া-দাওয়াও ঠিক মতো করেননি। দরজা-জানালা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসে শুধু ভেবে গেছেন, কী দোষ ছিল লতার? কেন তাকে এত যন্ত্রণা সহ্য করে মরতে হলো?
নাঃ, এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর পাননি শান্তিদা। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন একটা কথা, নিকট জন চলে গেলেও জীবনটা কখনো থেমে যায় না। তাই এক মাস পর শান্তিদা আবার হোটেল খুললেন। লোকজন সব খেতে আসতে শুরু করলো। সব কিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেলো, কিন্তু শান্তিদা আর স্বাভাবিক হতে পারলেন না।
তবুও পৃথিবী তার স্বাভাবিক নিয়মেই ঘুরতে থাকলো। দিন কাটতে লাগলো। বছর ঘুরতে লাগলো। শান্তিদার চুল-দাড়িতে পাক ধরলো। চোখে মোটা কাচের চশমা উঠলো। শান্তিদার মেয়ে টুনির বিয়ে হয়ে গেলো আর ছেলে মন্টু কলেজ পাশ করলো।
শান্তিদা ঠিক করেছিলেন, ছেলেকেই হোটেলের দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু, তাঁর ভাবনা আর বাস্তবের মধ্যে আকাশ-পাতাল অন্তর ছিল। মন্টু ঠিক করলো, সে সরকারি চাকরি করবে, শিক্ষক হতে পারলে ভালো হয়। শান্তিদা ছেলের ইচ্ছের কথা জানতে পেরে মহা ফাঁপড়ে পড়লেন। ছেলে চাকরি করলে হোটেল সামলাবে কে? কে তাহলে তাঁর ব্যবসার উত্তরসূরী হবে? কিন্তু মন্টু কোনো কথাই শুনতে নারাজ। তার পেটে বিদ্যে পড়েছে, তার চেতনার চোখ উন্মোচিত হয়েছে, তাই তার মুখে তখন বড়-বড় সব বুলি। ‘চাষার ছেলে চাষা হবে কেন?’ কিংবা ‘কে বলেছে, মজুরের ছেলেকে সেই মজদুরীই করতে হবে?’
কথাগুলো একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো ছিল না বলে শান্তিদাও আর লড়াই চালিয়ে যেতে পারেননি। মন্টু বাপের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সরকারি চাকরির একটা নামজাদা ট্রেনিং সেন্টারে যখন ভর্তি হলো, তখন শান্তিদা মনে-মনে শুধু বলেছিলেন, ‘যাই কর শুধু বংশের মান ডোবাস না…’
না, মন্টু বংশের মান ডোবায়নি। সে ট্রেনিং শেষ করে পরীক্ষা দিলো এবং প্রথম বারের চেষ্টাতেই চাকরি পেয়ে গেলো। মৌখিক পরীক্ষায় উতরে সে পোস্টিং পেলো সুদূর নামখানার এক হাই স্কুলে। শান্তিদা খুশিই হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।
যথা দিনে বাবাকে প্রণাম করে মন্টু একাই ব্যাগ-বাক্স ঝুলিয়ে নামখানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো। পাড়ায় ধন্যি-ধন্যি পড়ে গেলো। কলোনীর তরুণীরা যারা কোনোদিন মন্টুর দিকে ফিরেও তাকায়নি, তারাও সব শান্তিদার সরকারি চাকুরে সুপুত্রের সম্পর্কে খোঁজ-খবর শুরু করে দিলো আর শান্তিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গিয়ে বসলেন হোটেলে। এখন আর তাঁর কাছে এই হোটেলটা ছাড়া আপন বলতে কেউই রইলো না। শান্তিদা এই জীবনে বড় একা হয়ে পড়লেন।
মানুষ যখন একাকীত্বে ভোগে তখন ধীরে-ধীরে হতাশা তাকে গ্রাস করে। তীব্র মানসিক অবসাদের জালে সে জড়িয়ে যায়। সেই থেকে নানান রোগের জন্ম হয় শরীরে। শান্তিদারও তাই হলো। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।
হোটেলের কর্মচারীরা প্রমাদ গুনলো। পাড়ার লোক উদ্বিগ্ন বোধ করলো। তড়িঘড়ি খবর গেলো নামখানায়। হোটেলের নিয়মিত খদ্দের রঘুপতি টেলিফোনে তলব করলো মন্টুকে। কিন্তু মন্টু ততদিনে লায়েক হয়ে গিয়েছে। ইস্কুলের রাজনীতিতে তার হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে স্থানীয় একটি মেয়ের সাথে তার প্রেম সম্পর্কেরও সূচনা হয়েছে। তাই মন্টু এক কথায় জানিয়ে দিলো, সে যেতে পারবে না…
রঘুপতির মুখে খবরটা শুনে অসুস্থ শান্তিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াতে লাগলো। কোনোমতে তিনি তাঁর খাস কর্মচারী নগেনের হাত ধরে অনুরোধ করলেন ভাই গোপলকে খবর দিতে।
দাদার অসুস্থতার খবরে সত্যি বলতে, গোপাল একটুও বিচলিত হয়নি। সে ততদিনে পোড় খাওয়া একজন ব্যবসায়ী বনে গিয়েছে। তাই সাত-পাঁচ হিসেব করে পরদিনই সে সস্ত্রীক শান্তিদাকে দেখতে এলো।
শান্তিদা এত বছর পর ভাইকে দেখতে পেয়ে বড্ড খুশি হলেন। গোপালও অনেক মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে লাগলো। তারপর পিঠে বউয়ের চিমটি খেয়ে আসল কথাটা পেড়ে বসলো।
শান্তিদা বুঝতে পেরে গেছিলেন, তাঁর যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। এ-ও বুঝেছিলেন, হোটেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই গোপাল যখন মিনমিন করে হোটেলের দায়িত্ব নিতে চাইলো, তখন শান্তিদা আর আপত্তি করলেন না।
খাস জমিতে তৈরি হোটেল। তাই তার কাগজ-পত্তর বলতে কিছু ছিলো না যে হস্তান্তরের সই-সাবুদ হবে। মুখের কথাই এখানে শেষ কথা। আর সাক্ষী ছিল নগেন আর রঘুপতি। তাই পরদিনই গোপাল লোক-লস্কর এনে হোটেলের দখল নিয়ে ফেললো।
নগেন বাদে হোটেলের বাকি কর্মীরা সব ছাঁটাই হলো। হোটেল রঙ হলো। নতুন টেবিল-বেঞ্চ বসলো। নতুন রাঁধুনীও এলো। আর এসবের মাঝেই এক সন্ধ্যায় একা-একা মরে গেলেন শান্তিদা।
বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে বাধ্য হয়ে ছুটে এলো মন্টু। টুনিও স্বামীর সাথে এলো। দুই ভাই-বোন মিলে খুব খানিকটা কান্নাকাটিও করলো। তারপর শ্রাদ্ধ মিটতেই টুনি ও তার স্বামীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে মন্টু কাকার হাতে বাড়ির চাবি গুঁজে আবার রওনা হলো নামখানা।
ভাইপো বিদায় হতেই গোপালও লেগে পড়লো কাজে। সবাইকে চমকে দিয়ে সে লোক দিয়ে ‘শান্তিদার হিন্দু হোটেল’ লেখা রংচটা সাইনবোর্ডটা উপড়ে ফেলে দিল। তার জায়গায় বসলো নতুন বোর্ড, তাতে লেখা, ‘গোপালের হিন্দু হোটেল…’
মোটামুটি সবকিছুরই ভোগ-দখল করে ফেললো গোপাল। কিন্তু একটা জিনিসের দখল সে নিতে পারলো না। হোটেলের যতই নতুন নাম সে রাখুক না কেন, এলাকাবাসী এবং খদ্দেররা কিন্তু হোটেলকে তার পুরোনো নামেই ডাকতে লাগলো, ‘শান্তিদার হিন্দু হোটেল…’
গায়ের জোরে, ছল-চাতুরী করে অনেক কিছুই হয়তো দখল করা যায়। কিন্তু গা-জোয়ারি করে কিছুতেই মানুষের মনটা দখল করা যায় না। তার জন্যে দরকার পড়ে ভালোবাসার। যে ভালোবাসা জীবদ্দশায় বিলিয়ে গিয়েছিলেন শান্তিদা। তাই তো সাইনবোর্ড বদলালেও মুছে যায়নি শান্তিদার নাম।
শান্তিদার নাম মোছেনি, শান্তিদাদের নাম মোছে না…
লেখকের কথা: ঋক ঋকমন্ত্র
ঋক ঋকমন্ত্র একজন চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ লেখক। চিত্রনাট্য রচনার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত গল্প-কবিতা ইত্যাদি লেখালিখি করেন।
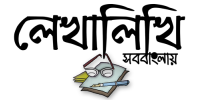


গল্পের বাঁধুনি আলগা গল্প বলার ধরনেও তেমন মুন্সিয়ানা নেই। অথচ বিষয় নির্বাচন চমৎকার।সম্ভাবনাও ছিল।
Asadharan
দারুন লিখেছিস
গল্পটা কেমন যেন জমতে জমতে ও জমল না।তবে এটা একান্ত ব্যক্তিগত মতামত।
এরকম অনেক ঘটনা রাস্তাঘাটে দেখি আমরা, সেটাকে আমাদেরই বলার ধরণে আমাদেরই আবেগ মিশিয়ে উপস্থাপনে কখন যেন সত্যি হয়ে গিয়েছে।
ভালো লাগলো…
বেশ ভালো লাগলো