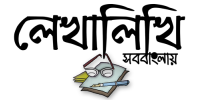লেখক : রানা চক্রবর্তী
হেমেনের আঁকা নারীর শরীরে যৌনতার আভাস আছে। ভেজা শাড়ির ওপর ফুটে ওঠা নারীর শরীরের ভাঁজ, বাঁক, পেশি, হাড় মুগ্ধ নয়নে দেখবেন যেকোনো পুরুষই, এমনকি অনেক নারীও চোখ ফেরাতে পারবেন না নিশ্চিত। এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় আছে, হেমেনের আঁকা নারীরা কেউই ষোড়শী বা অষ্টাদশী উদ্ভিন্নযৌবনা নন; বরং তারা বেশ প্রাপ্তবয়স্ক এবং মনে হয় বিবাহিতা। দি উন্ডেড ভ্যানিটি, ব্লু সারি, হারমোনি ও ইমেজ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।
হেমেন নারীর শরীর ও নগ্নতাকে প্রাধ্যান্য দিয়ে আঁকলেও তার ছবিতে নারীকে পূর্ণ নগ্ন চেহারায় দেখা যায় না। তবে গায়ের কাপড় যেন আবরণের চেয়ে প্রকাশেই বেশি সাহায্য করে। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার লিখেছেন, ‘দেহের যে অংশে বসন লেগে আছে এবং যে অংশে বসন লেগে নেই তার মধ্যে রংয়ের শেড এর সূক্ষ্ম তারতম্য এনে যৌবন-লাবণ্যের আভাস দেওয়াতে তাঁর (হেমেন) জুড়ি ছিল না।’
হেমেন মজুমদার পরপর তিন বছর অভিজাত বোম্বে আর্ট সোসাইটি থেকে তিনটি পুরস্কার জেতেন। এর মধ্যে ১৯২১ সালে স্মৃতি শিরোনামের চিত্রকর্মটির জন্য তাকে স্বর্ণপদক দেয়া হয়। ১৯২২ সালে ‘বর্ণঝঙ্কার’ এবং ১৯২৩ সালে ‘কর্দমে কমল’ ছবির জন্য হেমেন পুরস্কার জেতেন। হেমেনের এ পদকপ্রাপ্তিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় বোম্বে ক্রোনিকালে সাংবাদিক কানহাইয়ালাল ওয়াকিল লেখেন, ‘কলকাতার এক হেমেন মজুমদার প্রদর্শনীতে তিনবার প্রথম পুরস্কার জিতেছেন। এটা বোম্বের শিল্পীদের জন্য মর্যাদাহানিকর… হয় এই জুরি বোর্ড অযোগ্য নয়তো প্রদর্শনীর জন্য জনাব মজুমদার বেশি যোগ্য।’
এ পুরস্কারগুলো জেতার পর স্বাভাবিকভাবেই হেমেনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় বিভিন্ন পত্রিকায় তার আঁকা ছবি ছাপা হতে শুরু করে। বোম্বে, মাদ্রাজ, সিমলা, দিল্লিসহ আরো অনেক শহর থেকে হেমেনের ছবি প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়। অনেক বিখ্যাত মানুষ এ সময় হেমেন্দ্রনাথের ছবি কিনতে শুরু করেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা পূর্ণচন্দ্র দুই বছরে হেমেনের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকার ছবি কিনেছিলেন।
১৯২৬ সালে হেমেন মজুমদার জীবনের প্রথম আর্থিক সাফল্য পেলেন—একটি কমার্শিয়াল ফার্ম বেশ ভালো মূল্য দিয়ে তার একটি ছবির রিপ্রডাকশন রাইটস কিনে নেয়। কোম্পানিটির বার্ষিক ক্যালেন্ডারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল হেমেনের ছবিটি।
হেমেন স্বল্পবসনা নারীর চিত্র আঁকিয়ে শিল্পী হিসেবে খ্যাতি কিংবা কুখ্যাতি অর্জন করেন। হেমেনের চিত্রকর্ম জয়পুর, বিকানের, কোটাহ, কাশ্মীর, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, পাটিয়ালা এবং অন্যান্য দেশীয় রাজাদের আকর্ষণ করে। এদের মধ্যে পাটিয়ালার মহারাজা স্যার ভূপিন্দ্রনাথ সিং (১৮৯১-১৯৩৮) ছিলেন সবচেয়ে নিবেদিত। কাশ্মীরের মহারাজা ১৯৩১ সালে হেমেনকে ছবি আঁকার জন্য তাঁর দরবারে নিয়ে যান। এরপর পাটিয়ালার মহারাজা স্যার ভূপিন্দ্রনাথ সিং পাঁচ বছরের জন্য মোটা বেতনে হেমেনকে রাজচিত্রকর হিসেবে নিয়োগ দেন। এ অর্থ দিয়ে তিনি কলকাতায় একটি স্টুডিও খোলেন।
হেমেন মজুমদার কী অর্জন করলেন? এ প্রশ্নের জবাব শোনা যাক বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক রানা মিত্রের লেখা থেকে—
হেমেন বাঙালি সৌন্দর্যের প্রকার তৈরি করেছিলেন, যা সেকালের বাঙালি জনতাকে সেগুলোর পরিচিত ভাব ও অকপটতার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছবিগুলো আর্ট স্কুল থেকে পড়ে আসা কোন শিল্পীর আঁকা নৈর্ব্যক্তিক ছবি ছিল না, বরং ছিল অনুভবযোগ্য, শ্বাস নেয়া জীবন্ত নারী। ভারতীয় শিল্পে নারীচিত্রের ইতিহাস দীর্ঘ এবং জটিল। কোনমতে গায়ে ফেলে রাখা লাস্যময়ী অপ্সরা, ইয়াকশি থেকে ভারতীয় মন্দিরে দেবী মূর্তি। মন্দিরগাত্রে যৌনকর্মেরও প্রচুর ভাস্কর্য আছে। এসব অকপট দৃশ্য-ভাস্কর্য প্রাচীন সময়ের সাধারণ স্পিরিটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি হয়েছিল, পঞ্চম শতকের কবি কালিদাসের কবিতা-নাটকেও এমন অবাধ দৃশ্যের হাজিরা পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনের অবসানে শিল্পকলায় নারীর উপস্থাপনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হাজির হয়। মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবে ‘অভিজাত/সম্মানিত’ নারী বিবসনা হয়ে আর সামাজিক পরিসরে হাজির হতে পারলেন না। কিন্তু কৃষক সমাজে এই সংস্কৃতির বাধা ছিল না। আবার কেরালার নায়ার সমাজের অভিজাতদের ওপরও এসব নিষেধাজ্ঞার কোন প্রভাব ছিল না, তাঁরা বিশ শতকের শেষভাগেও উন্মুক্ত বক্ষে চলাফেরা করতেন। তুর্কি-আফগান থেকে মোগল আমলে মিনিয়েচার চিত্রকর্মে নগ্ন নারীর দেখা পাওয়া যেত না বললেই চলে। শুধু ব্যতিক্রম ছিল রাজস্থান ও পাহাড়ি মিনিয়েচার।
পরিস্থিতি একেবারে বদলে যায় ব্রিটিশ রাজের শাসনামলে। উনিশ শতকে খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের বিবেচনায় হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন অনৈতিক বিষয়ের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা শুরু করে। ভিক্টোরীয় এভানজেলিজমের প্রভাবে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা পোশাক, আচরণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতাবাদী মনোভাবে গ্রহণ করে—নারীর সজ্জায় যুক্ত হয় ব্লাউজ, পেটিকোট।
এমন পরিস্থিতিতে শিল্পকলায় দেহের উপস্থাপনা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়। ইংরেজরা হিন্দু মন্দিরের নগ্ন ভস্কর্যকে অনুমোদন না করলেও ভিক্টোরিয়ান অ্যাকাডেমিক ন্যুড আর্টকে সম্মান জানাত।…শাসকরা শালীনতার নতুন ধারণাকে চাপিয়ে দিলেন। শালীনতা বজায় রেখে শরীরের কতটা প্রদর্শন করা যাবে তা নির্দিষ্ট করা হল।
পাশ্চাত্য রীতিতে কাজ করা ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পী হলেন রাজা রবি ভার্মা (১৮৪৮-১৯০৬)। তিনি নারীর সৌন্দর্য প্রকাশে একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে নগ্নতা ছিল একেবারেই দুর্লভ। এদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে (১৮৭১-১৯৫১) বেঙ্গল স্কুল অব পেইন্টিং ফিগার ড্রইংকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
হেমেন তাঁর আঁকার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন গোসল শেষে ভেজা কাপড়ে বাড়ি ফিরতে থাকা পল্লী গাঁয়ের কুমারীকে। এতে তিনি ভেজা পোশাকের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠা নারীর শরীরকে উপস্থাপনার সুযোগ পান। অবশ্য হেমেন এসব কাজ করেছিলেন স্টুডিওতে বসে। এজন্য তিনি আলোকচিত্রের সহায়তা নিতেন। এভাবে তিনি ভারতে ফিগার পেইন্টিং এর একটি নতুন রীতি উদ্ভাবন করেন—আধা স্বচ্ছ কাপড়ের ওপর ফুটে ওঠা আবেদনময় মাংসল শরীরের রেখা। রাজা রবি ভার্মার ভাই রাজা ভার্মা এ বিষয়ে প্রথম কিছু কাজ করেছিলেন কিন্তু সেগুলো জনপ্রিয় হয়নি কিংবা পরবর্তী শিল্পীরা তাঁকে আর অনুসরণ করেননি। এদিকে হেমেন একটি স্বতন্ত্র রীতি তৈরি করেছিলেন এবং তার কিছু অনুসরণকারীও সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। হেমেনকে অনুসরণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পাঞ্জাবের ঠাকুর সিং। হেমেন উজ্জ্বল রংয়ের অভিজাত বাঙালি নারীর যৌন আবেদনকে ক্যানভাসে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। খুব সম্ভবত তার আঁকা বিভিন্ন নারীচিত্রের প্রেরণা ছিলেন তার স্ত্রী, তবে ছবির মডেলে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে তেমন সাদৃশ্য রাখেননি।”
হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তার হাতে লেখা কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যা ‘ছবির চশমা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নামটি তিনি নিজেই লিখে রেখেছিলেন। এসব লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে হেমেন লিখেছিলেন—‘দুনিয়ার সব বিদ্যারই পরীক্ষা আছে। জহুরী জহর চিনিতে পারে—কাচ ও কষ্টিপাথরের সাহায্যে, বিজ্ঞানের দান—অশেষ পরীক্ষারই ফল, সঙ্গীতের পরীক্ষক—নিপুণ শ্রবণেন্দ্রিয়, আর কলাবিদ্যার পরীক্ষক—অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি। দৃষ্টিহীনতায় চশমার ব্যবহার আবশ্যক, তাই ছবির চশমার সৃষ্টি।’
মানবজীবন-সমাজে শিল্পের গুরুত্ব, অবস্থান নিয়ে হেমেন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। ছবি আঁকায় তিনি বেছে নিয়েছিলেন তেল রঙ, যা তৎকালের ভারতীয় শিল্পীদের কাছে পাশ্চাত্য রীতি বলে অচ্ছুত। হেমেনের কথায়, “‘ভারতীয় পদ্ধতি’র দল বলবেন, তৈলচিত্রটা বৈদেশিক সম্ভার, তাহাতে আলেখ্য নির্মিত হইলে তাহা খাঁটি ভারতীয় হয় না ইত্যাদি…এসব অপযুক্তির কোন মূল্য নাই।…আমাদের ‘ভারতীয় পদ্ধতিওয়ালাগণ’ বক্তৃতার সময় গোঁড়ামির চরমে যান, কিন্তু পরিধানে সেই মিলের বস্ত্র—মুখে ‘কেপসেটন’ সিগারেট ও বাহনটি হাওয়াগাড়ি।…অতীত গৌরবের দৃষ্টান্ত যে জাত মুহুর্মুহু দেয় আর বর্তমানে যে পঙ্গু সাজিয়া অজ্ঞতার আড়ালে মুখ লুকাইয়া বসিয়া থাকে; নিজে অক্ষম, দেশের অন্যান্যেরা যদি কিছু আশার আলো আনে তবে সে আলো বৈদেশিক তাহা সনাতন নয়, তাহা রীতিবিরুদ্ধ ইত্যাদি বলিয়া সে আলোকে ফিরাইয়া দিতে বলে তাহারা ভণ্ড—তাহারা মূর্খ। তাহারা অন্তরে ঠিক জানেন তৈলচিত্র অতি উচ্চাঙ্গের জিনিস।”
আগেই আলোচনা হয়েছে কীভাবে অবনীন্দ্রনাথের মতো প্রভাবশালী মানুষ এবং স্থানীয় রীতির আধিপত্যের সঙ্গে হেমেনকে লড়তে হয়েছে। খুব সম্ভবত ঔপনিবেশিক শাসনে পাশ্চাত্যের চিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যে দর্শন, সেটা হেমেনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। স্বদেশী রীতি মানতেই হবে—এমন কোনো সংস্কারে তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন না। শিল্পীর স্বাধীনতাকেই হেমেন সবার আগে স্থান দিয়েছেন—‘শিল্পী বা কবির কল্পনা যেমন তাহার স্বাধীন চিন্তার ফল তেমনি সেই কল্পনাকে রূপদান করিবার প্রণালী বা পদ্ধতিও তাহার নিজস্ব নৈপুণ্য। বলা বাহুল্য, নানা মুনির নানা মতের ন্যায় প্রত্যেক শিল্পীর অঙ্কন পদ্ধতি অপর যে কেহ অপেক্ষা ভিন্ন। লক্ষ শিল্পীর লক্ষ পদ্ধতি। কবির কাব্যসৃষ্টি যদি হুকুমের অপেক্ষা রাখে তবে সে কাব্য পড়িবার পূর্বেই অপাঠ্য। তেমনি শিল্পী যদি তাহার শিল্প-নির্মাণ-কার্যে আদেশের অধীন হয় তবে সে চিত্র অঙ্কিত না হইলে ক্ষতি কী?’
তৎকালীন সমাজে চিত্রকর্মের এবং শিল্পীর কদর কেমনতর অবস্থায় ছিল তা পাওয়া যায় হেমেনের লেখায়। নিজেদের দোষগুলোকে হেমেন ক্ষমাহীন বাক্যে উদোম করে দিয়েছেন—‘আমরা ইংরেজের সঙ্গে মিশিয়া তার সদগুণ যে পরিমাণ গ্রহণ করি কুগুণ সংগ্রহ করি তার দশ গুণ। গরীব হইয়াও আমরা ভাল খেতে না পাইলেও ইংরাজী সভ্যতায় মোটরগাড়ি চড়াটা নকল করিয়াছি। কিন্তু সাহেবের ধৈর্য সাহস ও স্বধর্মপ্রীতি শিখিলাম কৈ? এইখানেই রুচির ও সভ্যতার পরীক্ষা। চিত্রপ্রীতির কথা বলিলেই দেশের সকলে একবাক্যে বলিবে—‘অতি গরীব দেশ— ছবি কিনিবার পয়সা কোথায়? কিন্তু যে ব্যক্তির ঘোড়ার গাড়ি চড়াও কর্তব্য নয় তিনি কিনিবেন চার হাজার টাকার মোটরকার! অথচ একশত টাকায় এখানে চিত্র কিনিতে উপরের ঐ যুক্তি প্রদর্শন।’
তিনি ছবি আঁকার কার্য প্রকারণে আলোড়ন তুলেছিলেন শাস্ত্রবিরোধিতায়। জলরঙ নয়, তাঁর ছবি আঁকার মাধ্যম ছিল তেলরঙ। পশ্চিম ইউরোপের ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পীদের মতো বড়ো ক্যানভাসে তিনি তেলরঙের পৌরুষ দেখিয়েছেন। নিসর্গচিত্র নয়। তাঁর বিষয় ছিল মানুষ। মানুষের মুড। মানুষের ভঙ্গিমার কাব্যময়তা। হেমেন্দ্রনাথের কাজের এই পরিধি কলকাতায় সে সময় বলার মতো একটা ঘটনা ছিল। কারণ তাঁর ছবিতে কোথায় জলরঙ? কোথায় নিসর্গ চিত্র? কিংবা ধর্মীয় শিল্পবোধ?
এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সমসাময়িক ছবির জগতে তাঁকে এক বৈপ্লবিক সংঘর্ষের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বস্তুত তখনকার দিনে মডেলহীন, উপকরণহীন চিত্রচর্চার কালে দেব–দেবীর ছবি আর পাহাড়, নদীর ছবি ছাড়া মানুষ আঁকবেনই বা কী? আর যদি পোর্ট্রেট আঁকতেই হয়, তবে দেশনেতার ছবি কিংবা পরিবারের লোকজনদের ছবি আঁকাই তো ভারতীয়তা? এই ছিল সেদিনের স্বাভাবিক প্রবণতা। আর তার কারণও ছিল বিস্তর।
আমাদের চিত্রশিল্প, সাহিত্যে তখন লেগেছে ইংরাজি ধরণ। ভিকতোরিয়ান মূল্যবোধ। বঙ্গিমী সাহিত্যে বায়রন, শেলিদের উক্তি। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিম শেষ বাক্যে এসে ভিকতোরিয়ান মূল্যবোধের শিকার হলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি আর শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন গুস্তভ ফ্লবেয়রের মাদাম বেভারী কিংবা ভলতেয়রের ক্যান্ডিট হতে ব্যর্থ হল। আর চিত্রকলায় ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথের হাতে সৃষ্ট হল ভারতমাতা । বঙ্কিমের বন্দেমাতরম–এর মতোই অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা দেশোদ্ধারে নিবেদিত মানুষের কাছে আত্মচেতনার প্রতীক হয়ে উঠল। ইংল্যান্ডের ভিকতোরিয়ান মূল্যবোধে আঁকা ছবিগুলোর মতো এদেশের শিল্পীরা নারী শরীরের ছবি আঁকলেন। প্রোফাইলে নয়, যেখানে শরীরের বিপদজনক ভাঁজগুলো চিহ্নিত হয়। সামনা–সামনি, যেন দ্বিমাত্রিক। আর নারী শরীরের মুখ ছাড়া বাকি সবটাই পোশাক আবরিত। অর্থাৎ কাম–প্রেমহীন ক্যালেন্ডারের দেবী ছবির মতোই অনুভূতিশূন্য করে আঁকা হতে থাকল নব্যভারতীয় শিল্পবোদের নারী শরীর।
অথচ আমাদের দেশের মেয়েরা তখনও ইউরোপীয় মেয়েদের মতো ব্লাউজ, সেমিজ, পেটিকোট পড়তে শেখেনি। তারা জানে না অন্তর্বাসের মাহাত্ম্য। আমাদের গ্রামদেশের মেয়েরা তখন অন্তঃপুরবাসিনী। তারা যদি কোন বিশেষ কারণে ঘরের বাইরে যায়, তাদের বাহন হয় পালকি। নতুবা ছই ঢাকা গরুর গাড়ি। তখনকার বাংলার গাঁ–দেশে, এমনকি শহর কলকাতায় প্রায় অক্ষরহীন মেয়েরা পথের ধারে বনফুলের মতো বেড়ে উঠেছিল। এদের কথা শরৎচন্দ্র রাখঢাক করে যেটুকু আমাদের জানিয়েছেন, তাই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক চেষ্টা। তাঁর মতো এত গভীর আর গোপনভাবে কেই বা আমাদের মেয়েদের কথা লিখেছেন?
হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ঠিক তেমন করেই তাঁর ছবিতে মেয়েদের, গ্রাম্যবালাদের অমর রেখে গেছেন। আমাদের মেয়েদের যৌনতাবোধ (সেক্সুয়ালিটি) তাঁর ছবিতে যেভাবে উঠে এসেছে, তেমনভাবে তখনকারকালে অচিন্তনীয়ই ছিল। তাঁর পল্লিপ্রাণ, স্নানান্তে, সিক্তবসনা, সজ্জা সমাপন, পরিত্যক্তা, তন্ময়, সদ্যস্নাতা, বর্ষা এবং আরও বহু বহু ছবিতে রয়ে গেছে প্রাণোদিত এই যৌনতাবোধ। যা দর্শনে অশ্লীলতা নয়, বুকে জন্ম নেয় প্রগাঢ় প্রেম। মায়া। আমাদের ঘরের মেয়ে, যে নাবালিকা বয়সে বাপের ঘর ছেড়ে শ্বশুর ঘরে এসেছে। যৌবন শুরুর আগেই যে একাধিক সন্তানের মা। ভোর থেকে মাঝরাত সংসারের সব কাজ, অকাজের দায়িত্ব সামলানোর ফাঁকে যার মনে ফাঁকি পড়ে গেছে। সেই মেয়ে যখন পুকুরে সদ্য স্নান সেরে এক খণ্ড ভিজে কাপড়ে কাঁখে কলসি নিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে বাড়ি ফিরছে তখন আকাশে উল্লাসিত রোদ্দুর, বাতাসে উচ্ছ্বসিত ফুলের গন্ধ। বড়ো স্নিগ্ধ। বড়ো সজল। বড়ো মায়ামায় সেই যৌনতাবোধ।
নব্যভারতীয় শিল্পচর্চার প্যারাডক্স হিসেবেই তখন প্রতিভাত হয়েছে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৃষ্টি। অথচ, স্নান ও নারী এ দুটো বিষয়কে এক করে ছবি আঁকা হেমেন্দ্রনাথ প্রথম চালু করেছিলেন তা নয়। ইউরোপে নারীর এই গোপন ও ব্যক্তিগত প্রাত্যহিকী বহুকাল ধরে চিত্রের বিষয়। আমাদের দেশে রাজা রবি বর্মা কিংবা বামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সদ্য স্নানার ছবি এঁকেছেন। তবে বিষয় হিসেবে তাঁরা কেউই এমন সত্যনিষ্ঠ অলৌকিক শিল্প সৃষ্টি করতে পারেননি। বোধহয় হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারই প্রথম শিল্পী, যিনি ভারতীয় মেয়েদের একান্ত বস্তুনিষ্ঠ ছবি এঁকেছিলেন। ফলে তাঁর ছবিতে এসেছে নাটকীয়তা। এসেছে নারীর একাকীত্ব। ঘরের বাইরে, কিংবা ঘরের ভেতরে তাঁর ক্যানভাস যখনই কোন নারীর সন্ধান করেছে, তখনই দেখা গেছে সেই নারী বিবাহিতা, সংসারি হওয়া সত্ত্বেও একা। তার একাকীত্বই হয়েছে হেমেন্দ্রনাথের ছবির মূল সুর।
হেমেন্দ্রনাথ ইডেন গার্ডেনসে অল ইন্ডিয়া একজিবিশনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। এতেই শরীর ভেঙে গেল। ১৯৪৮ সালের ২২ জুলাই তিনি অকাল প্রয়াত হন।
প্রথা ও শাস্ত্র বিরোধী হেমেন্দ্রনাথ অবশ্যই ব্রাত্য ছিলেন নব্যভারতীয় চিত্রকালের ভুবনে। তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার নিজের বিশ্বাসে ছিলেন স্থির। উদ্ভাবনী শক্তিতে ছিলেন দৃঢ়। ছিলেন এক বগ্গা। তাঁর মননে ভারতমাতা (আদিতে যার নাম ছিল বঙ্গমাতা ) হল গাঁ–দেশের একান্ত আটপৌড়ে মেয়েরা। যারা একাকিনী। যাদের বুক ফাটলেও মুখ কোনদিনও ফোটে না।
(তথ্যসূত্র:
১- হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, অনুরাধা ঘোষ, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ।
২- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা এপ্রিল ২০১৭ সাল।
৩- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে আগস্ট ২০১৬ সাল।)
লেখকের কথা: রানা চক্রবর্তী
রানা চক্রবর্তী পেশায় সরকারী কর্মচারী। নেশা ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা আর লেখালিখি। নিজেকে ইতিহাসের ফেরিওয়ালা বলতে ভালবাসেন।