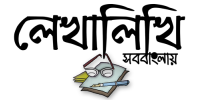লেখক: রানা চক্রবর্তী
সুযোগ পেলেই কুটুস কুটুস। কাউকে ছাড়ি না। আমাদের কামড় খাওনি কে? এক্ষুনি এসো, একটা দিচ্ছি কুটুস করে। জেনে হোক বা না-জেনে, তোমরাও তো আমাদের মারো পিষে পিষে। আমরা তোমার ঘরের কুটুম অথবা প্রতিবেশী। কত যেন নাম আমাদের। যেমন ধরো, পিঁপড়ে, পিঁপড়া, পিঁপিড়া, পিপীলি, পিপীলিক, পিপীলিকা। আকার, গায়ের রং, অবস্থান ইত্যাদির বিচারে আমরা কেউ লাল পিঁপড়ে, কেউ কালো, কেউ কাঠপিঁপড়ে, কেউ ডেঁয়ো। আমরা সবাই কিন্তু কামড়ুটে নই, কেউ কেউ খুব নিরীহ। অনেকেই আবার লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকি। তবে হে মনুষ্যগণ, তোমরাও সবাই খারাপ নও। কেউ কেউ আমাদের কথা ভেবেছ, আমাদের নিয়ে লিখেছ। তোমাদের যিনি সবচেয়ে বড় কবি, সেই রবীন্দ্রনাথ কত ছোটবেলায় আমাদের না-খেতে পাওয়ার কষ্ট বুঝেছিলেন। তাই তো লিখে গেছেন—
“আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে…
হাপুস হাপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।”
কবি অমিয় চক্রবর্তীও আমাদের প্রতি খুব দরদি ছিলেন। তিনি লিখেছেন দরদভরা কবিতা –
“আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ওই ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোট পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক।”
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ‘কাজের লোক’ ছড়াটা তো অনেকেই পড়েছ। সেখানে মৌমাছি, পাখি আর আমাদের কাজকর্মের কথা বলা হয়েছে। ছোট খোকা বলছে—
“পিপীলিকা পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও,
যাও ভাই বলি।”
পিপীলিকা অর্থাৎ আমাদের এক জন উত্তরে বলছে—
“শীতের সঞ্চয় চাই,
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।”
কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কী লিখেছেন, শুনবে? তিনি লিখেছেন—
“পিঁপড়ে
ভাঁড়ার ঘরে কী করে?
এটা খায় ওটা খায়
পিঁপড়েনিকে গান শোনায়।”
আমাদের বিষয়ে প্রবাদ, ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ কিছু কম লেখা হয়নি। গিরীন্দ্রশেখর বসু তো বিরাশি বছর আগে একটা আস্ত বই-ই লিখে গেছেন। বইটার নাম ‘লালকালো’। ঘোষদের পুরনো ডোবার এক পারে কালো অন্য পারে লালদের বাস। দু’দলের লড়াই নিয়ে এক দারুণ মজার কাহিনি আছে বইটাতে। তোমাদের গর্বের বাঙালি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের জীবনযাত্রা নিয়ে নিবিড় গবেষণা করেছেন। ‘বাংলার কীটপতঙ্গ’ বইয়ের প্রথম চারটে অধ্যায়ে তিনি আমাদের কথা লিখেছেন। যেমন, ‘শ্রমিক পিঁপড়ের জন্মরহস্য’, ‘পিঁপড়ের বুদ্ধি’, ‘পিঁপড়ের লড়াই’, ‘ক্ষুদে পিঁপড়ের ব্লিত্সক্রিগ’। ‘ব্লিত্সক্রিগ’ মানে সমরনীতি বা রণকৌশল। গোপালবাবু পদে পদে আমাদের শ্রম, নিষ্ঠা আর বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন।
আমাদের বিষয়ে কত জন কত কিছু লিখেছেন। দেশ-বিদেশে কত গবেষণা হয়েছে। সেই সব গবেষণা থেকে এমন তাজ্জব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা আমরাও জানতাম না। দু’একটা বলি, শোনো। আমরা পৃথিবীর তেরো কোটি বছরের পুরনো বাসিন্দা। সারা বিশ্বে আমাদের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজার ট্রিলিয়ন। ট্রিলিয়ন মানে জানো তো? এক লক্ষ কোটিতে হয় এক ট্রিলিয়ন। আমরা প্রায় সাড়ে বারো হাজার প্রজাতিতে বিভক্ত। জলের নীচে চোদ্দো দিন বেঁচে থাকতে পারি। সারা দিনে মাত্র কয়েক মিনিট ঘুমোই। আমরা কলোনি বানিয়ে অনেকে মিলেমিশে থাকি। কলোনি ছাড়া একক ভাবে থাকতে পারি না। অবশ্য জানি, তোমরা গুণমান এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ তুলবে। সে যা হোক, আমরা ছোট বলে হেয় কোরো না। আমরা কিন্তু নানা ভাবে জীবজগতের উপকার করি। জীববৈচিত্র রক্ষায়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আমাদেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্র হতে পারি কিন্তু তুচ্ছ নই। আমাদের কাছ থেকেও শেখার আছে অনেক কিছু। কি, ছোট মুখে বড় কথা বলে ফেললাম না তো?
জীবনযুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় সবাইকে। কীট-পতঙ্গ যে প্রতিদিন লড়াই করে বেঁচে থাকে, এ দেশে তা প্রথম দেখেছিলেন বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। সবাই তাঁকে বলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী। প্রজাপতি, পিঁপড়ে, মাকড়সা, মাছ, ব্যাঙাচি – এসব নিয়ে তাঁর গবেষণা। পিঁপড়েরও কত নাম। বিষ পিঁপড়ে, কাঠ পিঁপড়ে, লাল পিঁপড়ে, সুড়সুড়ে পিঁপড়ে, ডেঁয়ো পিঁপড়ে, নালসো পিঁপড়ে, ক্ষুদে পিঁপড়ে – এদের স্বভাব হল লড়াই করে বেঁচে থাকা। যুদ্ধ করে জয় ছিনিয়ে নেওয়া। যুদ্ধ জয় করে এরা আনন্দে নাচে। যুদ্ধে জেতার প্রবণতা ক্ষুদে পিঁপড়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ক্ষুদে পিঁপড়ের দল মাটি দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে। তারপর উই পোকার মতো মাটির নিচ দিয়ে গর্ত করে সুড়ঙ্গ বানায়। তারপর ছক কষে কিভাবে শত্রুকে বিনাশ করতে হবে। আর এই লড়াই তারা করে কেবলমাত্র খাবারের জন্য। তারা মূলত লড়াই করে বড় লাল পিঁপড়েদের সঙ্গে। গোপাল চন্দ্র বলছেন, ক্ষুদেদের কাছে প্রায়ই হেরে যায় বড়রা। আরও আশ্চর্য হল যে, যুদ্ধে জিতে পরাজিত কিছু পিঁপড়েকে তারা কয়েদ করে নিয়ে আসে। ছোটদের বাসায় ক্রীতদাস হিসাবে থাকে। শ্রমিকদের গোলাম হয়ে থাকে আজীবন।
গোপাল চন্দ্রের আগে থেকেই বিশ্বের নানা প্রান্তে কীট-পতঙ্গ নিয়ে গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানী ওয়সন, উইয়সন, গুডল গোয়ৎস বহু তথ্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গোপাল চন্দ্র যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা অনেকের কাছে ঈর্ষার কারণ। তাঁর গবেষণা থেকে অনেকে অনেক তথ্য নিয়েছেন। কেউ ঋণ স্বীকার করেছেন, কেউ করেননি। তবে তা নিয়ে তিনি কোনদিনই ক্ষোভ জানাননি।
তাঁর গায়ে সোঁদা মাটির গন্ধ। কবিগান গেয়ে বেড়িয়েছেন, লোকগীতি গেয়েছেন। ভাটিয়ালির সুর তুলেছেন, গ্রামের কৃষক, শ্রমিকের জন্য গান লিখেছেন। এরই সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন বাংলার বনে-জঙ্গলে। কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করেছেন। খালি চোখেই তাঁর দেখার ক্ষমতা ছিল আশ্চর্য। খাবারের জন্য কীট-পতঙ্গরাও যে মানুষের মতো যন্ত্র ব্যবহার করে তা এদেশে তাঁর আগে আর কেউ দেখতে পাননি। বিদেশে যে এসব নিয়ে কাজ হচ্ছে তা তিনি জানতেন না। বাবা মারা গিয়েছিলেন পাঁচ বছর বয়সে। মাকে নিয়ে সংসার চালাতে যজমানি করতে হত। পত্রপত্রিকা পড়বেন কী করে!
বিজ্ঞানী ডারউইন বলেছিলেন, গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জে এক শ্রেণির পাখি গর্ত থেকে পোকা বের করার জন্য গাছের ডালের সাহায্য নেয়। বিজ্ঞানী গুডল বলেছিলেন, শিম্পাঞ্জিরা উইপোকার গর্তে ঢুকিয়ে দেয় গাছের ডাল, সেই ডাল বেয়ে উই উঠে পড়ে আর তা খায় তারা। এ তো গেল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বাঁচার চেষ্টা। অমেরুদণ্ডীরাও যে বেঁচে থাকার জন্য যন্ত্র ব্যবহার করে তা দেখতে পেয়েছিলেন গোপাল চন্দ্র। তিনি বলেছিলেন কানকাটারি পোকা ডিম রক্ষা করার জন্য কী চেষ্টাই না করে। কানকাটারি পিছনের পায়ে কাদা মেখে শুকিয়ে নেয়, শত্রু এলে জোড়া পায়ে লাথি মারে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকে রক্ষা করার চেষ্টা। বিজ্ঞানী বলছেন ডিম পাড়ার পর কানকাঠারির পা দুটো জল ঢেলে ধুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মা হওয়ার কী বাসনা তার! পায়ে আবার সে কাদা মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নিয়েছে। ডিমের সঙ্গে নিজেকেও শত্রুর হাত থেকে সে বাঁচাতে চায়। মাকড়সা নিয়ে তাঁর গবেষণায় মুগ্ধ বিদেশের বিজ্ঞানীরা। মাকড়সা নিয়ে তাঁর গবেষণা দেখতে এসেছিলেন বেলজিয়ামের এক বিজ্ঞানী। মিলনের পর স্ত্রী মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে। মিলনের পর পালাতে যায় পুরুষ আর তখনই তাকে দৌড়ে ধরে ফেলে স্ত্রী। তারপর মেরে গিলে নেয়। গোপাল এই দৃশ্য দেখিয়েছিলেন বেলজিয়ামের বিজ্ঞানীকে, তিনি তো দেখে ‘থ’। বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসুর সহযোগী। তবে তা অনেক পরে। মাকড়সার স্বভাব কেন এমন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি।
দেখার চোখ, অনুসন্ধিৎসু মন, আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় এবং নিরন্তর অনুশীলন এই গুণগুলির সহাবস্থান যে কোনও মানুষকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। দারিদ্র্য বা উচ্চতর ডিগ্রির অভাব কোনও প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না তা বারে বারেই প্রমাণ করেছেন অনেকের সঙ্গে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ।
বেশ কিছু কাল আগের কথা বলছি। শরীয়তপুরের লোনসিং নামের একটি গ্রামে বাস করতেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নাম অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য। পেশা যজমানি। অর্থাৎ পুজোর দক্ষিণার দাক্ষিণ্যই তাঁর সংসারযন্ত্রকে সচল রাখতে সাহায্য করত। তবে মধ্যে কাজ করতেন স্থানীয় জমিদারের কাছারিতেও । তাঁর পরিবারেই ১৮৯৫ সালের পয়লা আগস্ট গৃহিণী শশিমুখী দেবী জন্ম দেন এক পুত্র সন্তানের। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তানটির কথাই আজকে বলতে বসেছি। তাঁর নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই সম্ভবত কীট আচরণ বিদ্যার পথিকৃৎ।
ছেলের যখন পাঁচ বছর বয়স, অম্বিকাচরণ পরলোক গমন করেন। বাড়ে দারিদ্র্যের মাত্রা। দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র্যের এই কষাঘাত গোপলাচন্দ্রের শৈশবকে কষ্টময় করে তুলেছিল। প্রতি মুহূর্তে জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁকে চলতে হতো। ছোটবেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাই হাইস্কুল শেষ করার পর তিনি যখন ১৯১৩ সালে কলেজে আই এ পড়ার জন্য ভর্তি হলেন তখন তাঁর আর কলেজ এর পাঠ্যক্রম শেষ করা হয়ে ওঠেনি। তবে স্কুলে থাকতেই তিনি কীট পতঙ্গের প্রতি আগ্রহী ওঠেন। কীটপতঙ্গের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে তাঁর জীবনীতে,
“ছেলেবেলার অনেক ঘটনার কথাই ভুলে গেছি, তবে কোন কোন ঘটনার অনেক কিছু স্মৃতিই রয়ে গেছে – কতক ঝাপসা, কতক পরিস্কার। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে যোগেন মাস্টারের কথা। মাঝে মাঝে যোগেন মাস্টার ছেলেদের ডেকে এনে ম্যাজিকের খেলা দেখাতেন। একটা মজার জিনিস দেখাবেন বলে একদিন তিনি ক্লাসরুমে মাস্টার, ছাত্র সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। পকেট থেকে গাঢ় খয়েরী রঙের কয়েকটি বিচি বের করে মাস্টারদের হাতে দিয়ে বললেন – দেখুন তো জিনিসটা কী এবং এতে কোন ছিদ্র বা টুটা-ফাটা আছে? দেখতে কতকটা কাঁই বিচির মতো হলেও আসলে তা নয়, কোনও একটা অজানা ফলের বিচি – মসৃণ ও গোলাকার, কোথাও কোনও টুটা-ফাটা নেই। বিচিগুলি টেবিলের ওপর রাখার কয়েক মিনিট পরেই একটা বিচি হঠাৎ প্রায় চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো। তারপর এদিক ওদিক থেকে প্রায় সবগুলি বিচিই থেকে থেকে লাফাতে শুরু করে দিল। অবাক কাণ্ড। কীভাবে এটা সম্ভব হতে পারে ? আমরা তো ছেলেমানুষ, বড়রাই কিছু বুঝতে পারেননি। অবশেষে মাস্টারমশাই ছুরি দিয়ে একটা বিচি চিরে ফেলতেই দেখা গেল, তার ভেতরে রয়েছে একটা পোকা (Larva)। টেবিলের ওপর পড়েই পোকাটা ধনুকের মতো শরীরটাকে বাঁকিয়ে দু-প্রান্ত একত্রিত করে এক অদ্ভুত ভংগিতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।
এই ঘটনা থেকেই কীট-পতঙ্গ, পোকা মাকড় সম্পর্কে একটা কৌতূহল জাগতে লাগল। নতুন কোনও পোকা-মাকড় বা গাছপালার কোনও বৈশিষ্ট্য নজরে পড়লে বিস্ময় জাগতো বটে, কিন্তু সুসংবদ্ধ জ্ঞানের অভাবে তার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল না।”
১৯১৩ সালে গ্রামের লোনসিংহ স্কুল থেকে জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৯১৪ সালে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। শহরে পড়াশুনার খরচ জোগানো সংসারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের ঝাপটা এসে পড়ল। ফলে পাকাপাকিভাবে পড়াশুনা বন্ধ করে গ্রামে যেতে হল। এখানে পণ্ডিতসার স্কুলে সহকারী শিক্ষকের পদে মাত্র ১৬ টাকায় শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। যখন তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন স্কুলে যাবার পথে, রাস্তার পাশে ছোট ছোট পোকামাকড়, তাদের জীবনযাত্রা খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি এই সব অভিজ্ঞতা, তার বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ করে তা লিপিবদ্ধ করতেন এবং প্রবাসী, ভারতবর্ষ সহ অন্যান্য পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করতেন।
স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় তাঁর সাহিত্যের প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি জারি গানও লেখা শুরু করেন । জারি ও পালাগান লেখার পাশাপাশি তিনি ১৯১৭ সালে “শতদল” নামক একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করা শুরু করেন, যা প্রতিমাসে প্রকাশিত হত। দুঃস্থদের জন্য কাজ করার একটি সংস্থাও গঠন করেন তিনি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য প্রকৃতির সংস্পর্শে এনে প্রকৃতির সাথে তাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন হাতেকলমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন সৃষ্টিকে উপলব্ধি করার জন্য। ‘সনাতন’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও এই সময়ে পালন করেন।
বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার প্রতি তাঁর যেমন আগ্রহ ছিল তেমনি তিনি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আগ্রহ তৈরি করতেন। কীটপতঙ্গের জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করতেন এবং ছাত্রদের প্রশ্নের সহজ ও সরল উত্তর দিতেন।
তাঁর গবেষণার নানাবিধ বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কীটপতঙ্গের গবেষণা। ছোট লাল পিঁপড়ে, নালসে পিঁপড়ে, মাকড়সা, শিকারি মাকড়সা, সাপ, ব্যাং, টিকটিকি, প্রজাপতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে অনেকে দেশে বিদেশে গবেষণা করে প্রতিষ্ঠিত হন, নোবেল পুরস্কার পান কিন্তু তিনি পাননি। ‘বাংলার কীটপতঙ্গ’ তার অন্যতম সেরা গ্রন্থ। ১৯৩০ সালে বাংলার মাছ খেকো মাকড়সা সম্বন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ জগদীশচন্দ্র বসুর নজরে পড়ে।
পিঁপড়ে অনুসারী মাকড়সা, টিকটিকি, শিকারি মাকড়সা সম্পর্কে বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি, সোসাইটি জার্নাল, আমেরিকার সায়েন্টিফিক মান্থলি, কলকাতার সায়েন্স অ্যান্ড কালচার-এ প্রকাশিত হয়। তাঁর মোট ২২টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়।
গোপালচন্দ্র যখন একা একা তাঁর গবেষণা করে যাচ্ছিলেন, তখন বিজ্ঞানের এই শাখার মূলধারাটি ছিল জার্মানিতে। যদি তিনি এই মূলধারার সঙ্গে মিলে যেতে পারতেন তাহলে তিনি হয়তো সারা বিশ্বে সুপরিচিত নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ত্রয়ী লরেঞ্জ, টিন বার্গেন ও ফন প্রিন-এর সমগোত্রীয় হয়ে যেতেন। তিনি চার্লস ডারউইন, জ্যাঁ অ্যারি ফ্যাবার, ওজিন মারেদের সঙ্গে এক সারিতে অবস্থান করতেন।
তাঁর জীবনী যদি পর্যালোচনা করা যায় তবে তাঁর কর্মগুলিকে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষিতে মহাকাব্যিক আখ্যা দেওয়াই যায়। তিনি পরবর্তী জীবনে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। যদিও তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকার কারণে তিনি অনেক সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। তবুও তিনি প্রকৃত অর্থেই মেধা মনন এবং মানসিকতার দিক থেকে ছিলেন একজন যুক্তিবাদী এবং কুসংস্কারবিরোধী ব্যক্তিত্ব। একথা তিনি তাঁর জীবন কথাতেই লিখে গেছেন –
“পূজার্চনা সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে মায়ের সঙ্গে প্রায়ই বাদানুবাদ হতো। একবার ভাইয়ের (মেজ ভাই নেপালচন্দ্র) ভয়ানক অসুখ হয়। ডাক্তার ও কবরেজ যখন আশা ছাড়লেন তখন একদিন স্বপ্ন দেখার ভান করে একটা ওষুধ মাকে দিলাম, ওষুধ ধারণ করার পর রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করে। এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ (করে) পদ্যছন্দে একটি ব্রতকথা লিখে ছাপিয়ে দিলাম। নাম ‘আপদ বিনাশিনীর ব্রতকথা’। বইটি ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো। এমন কি আজও বোধ হয় এই ব্রতকথা কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত আছে, প্রচারের পর মাকে সমস্ত বিষয়টা যে মিথ্যা তা খুলে বলি, এগুলির আসারতার কথা বুঝিয়ে দিলাম, অন্য লোকেদেরও বললাম, কিন্তু কেউ আমার এই সত্য কথা মানতে রাজি হননি।”
জগদীশ চন্দ্র বসু তাকে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কাজ করতে সুযোগ দেন সত্যি । তবে একটু ভালোভাবে তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করে দেখলে দেখা যায় কোন কোন স্থানে জগদীশ চন্দ্রের ব্যক্তিত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য গোপালচন্দ্রের কর্মের স্বাধীনতা প্রকাশের অন্তরায় দাঁড়িয়েছে।
সে যাই হোক। গোপালচন্দ্র প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ১৯৩২ সালে। ১৯৩৬ সালে তাঁর জলচর মাকড়সার ওপর কাজটি প্রকাশিত হয় American Museum of Natural History-এ এবং ১৯৫১ সালে আমন্ত্রিত হন International Union for the Study of Social Insects-এর সম্মেলনে। অনেক কাজের মধ্যে পিঁপড়ের লিঙ্গ নির্ধারণের পরীক্ষা এবং তার ভিতরে লুকিয়ে থাকা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে অন্যতম।
তিনি দলবদ্ধ পতংগ যেমন পিঁপড়া, মৌমাছি ইত্যাদির শ্রমিক, রাণী কীভাবে জন্মায়, তাদের প্রজনন, রূপান্তর, পূর্ণতা পাওয়া ইত্যাদি খুব বিচক্ষণতার সাথে লক্ষ করেন। তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলিতে পর্যবেক্ষণের দক্ষতার পরিচয় মেলে। ইংরেজি ভাষায় তাঁর রচনাকৃত পেপার সর্বমোট বাইশটি।
সত্যি কথা বলতে যে আমরা যে আজকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করছি, এই বাংলা ভাষাতে বিজ্ঞানচর্চা শুরু করা অন্যতম পথিকৃৎ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদান স্মরণ করছি অসম্ভব শ্রদ্ধা আর বিনয়ের সঙ্গে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্যে তিনি জীবনভর কাজ করেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি প্রায় ১০০০ এর মতো বিজ্ঞান বিষয়ে আর্টিকেল লেখেন যার বেশির ভাগই বাংলায় এবং তা প্রচুর জনপ্রিয়তাও পায়।
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সারা জীবনে হাজারের অধিক প্রবন্ধ লেখেন। বেশিরভাগই বাংলা পত্র পত্রিকায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবাসী, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর নতুনপত্র, মন্দিরা, সাধনা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গশ্রী, শিশুসাথী, সন্দেশ, নবারুণ, প্রকৃতি, নতুনপত্র, অন্বেষা, দেশ প্রভৃতি। গোপালচন্দ্র এই উপমহাদেশের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অনন্য পথিক।
গোপালচন্দ্র প্রথমে জগদীশচন্দ্র বসুর সহকারী হিসাবে পরে ‘স্যার জগদীশচন্দ্র বোস স্কলারশিপ’ নিয়ে ১৯২৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত টানা প্রায় ৪৮ বছর বসু বিজ্ঞান মন্দিরেই গবেষণার কাজে নিয়োজিত থাকেন।
তাঁর ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের রূপান্তরে পেনিসিলিনের ভূমিকা নিয়ে এই গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁকে অবসরের পরেও গবেষণা চালিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ১৯৫১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সামাজিক পতঙ্গ বিষয়ে আলোচনাচক্রে ভারতীয় শাখা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রিত হন।
১৯৪৮ সালে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাথে মিলে “বাঙ্গালী বিজ্ঞান পরিষদ” নামে একটি বিজ্ঞান গবেষনা সমিতি গঠন করেন।
পুলিনবিহারীর মতো কয়েক জন বন্ধু মিলে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৫০ সালে বাঙ্গালী বিজ্ঞান পরিষদের ম্যাগাজিন “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” এর অফিসিয়াল সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে তিনি এই ম্যাগাজিনের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি ভারতকোষ নামক বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরির সময় সহযোগী ভূমিকা পালন করেন।
তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচিত পুস্তকের মাঝে “বাংলার কীটপতঙ্গ”, “করে দেখা” (তিন খন্ড) অন্যতম। তাছাড়া তাঁর প্রতিটি রচনা একজন প্রকৃতিবিদ এবং যুক্তিবাদী হিসেবে তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় বহন করে।
১৯৬৫ সালে তিনি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং জ্ঞানের প্রতি তৃষ্ণা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার পটভূমির শুধু প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্বই নন তিনি হলেন অন্যতম। তাঁর লেখা আমাদের কাছে প্রেরণার এক অন্যতম আধার।
তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণের মধ্যে উভচরদের মেটামরফোসিস, বায়ো লুমিনেসেনস (bioluminescence) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তিনি কীট আচরণবিদ্যার উপর বিস্তারিত কাজ করেন। তিনি তাঁর কাজ দিয়ে হান্স মলিশ, হাক্সলির মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর জীবনব্যাপী যে সমস্ত বিজ্ঞানের বই লিখেছেন তার মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। তাঁর লেখা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হল—আধুনিক আবিষ্কার, মহাশূন্যের রহস্য, বাংলার কীটপতঙ্গ, মনে পড়ে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, করে দেখ, রোমাঞ্চকর জীবজগৎ, জীবন নিয়ে যে বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, বিষয় উদ্ভিদ ইত্যাদি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টির অফুরন্ত উৎস, তাদের মধ্যে এই শক্তিকে জাগরিত করার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের উৎসাহ দিতে হবে, যা গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর ছোটবেলা থেকেই। আনন্দ পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার ছাড়াও তিনি বহু সম্মানে সম্মানিত হন, তার সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর তিন মাস আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি এস সি সম্মানে ভূষিত হন।
১৯৮১ সালের ৮ এপ্রিল তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সত্যি কথা বলতে কি গোপাল চন্দ্রের মত অসাধারণ কিছু ব্যক্তিত্বের অবদান আমাদের আজকের দিনে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয়। তাঁর কর্মময় জীবন, বিজ্ঞানের প্রতি ছুটে চলার অপূর্ব আগ্রহ আর বিদগ্ধ এবং যুক্তিবাদী মানস ও মনন আমাদের সর্বদা প্রেরণা যোগাবে। আর উৎসাহ যোগাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে। তাঁর অসমাপ্ত কাজ, অপ্রকাশিত লেখা এবং তাঁর বাংলার কীট-পতঙ্গ সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে আজও দেশে বিদেশে বিভিন্ন গবেষক কাজ করে চলেছেন, আগামী দিনে এই সমস্ত গবেষক, প্রকৃতি বিজ্ঞানের গবেষণায় কোনও নতুন আলোর সন্ধান দিতে পারবে বলে আমরা আশা করে থাকব।
তথ্যসূত্র:
1. বিজ্ঞান অমনিবাস, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
2. বাংলার কীটপতঙ্গ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
3. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই এপ্রিল ২০১৫ সাল
4. বর্তমান পত্রিকা, ৯ই জুন ২০১৯ সাল
5. বঙ্গদর্শন
লেখকের কথা: রানা চক্রবর্তী
রানা চক্রবর্তী পেশায় সরকারী কর্মচারী। নেশা ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা আর লেখালিখি। নিজেকে ইতিহাসের ফেরিওয়ালা বলতে ভালবাসেন।