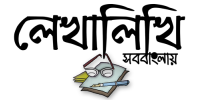লেখক : উজ্জ্বল চ্যাটার্জি
সবাই যে বলে – ঈশ্বর নিরাকার, ঠিকই বলে। প্রতি মুহূর্তেই তিনি আমাদের সাথে আছেন, বিভিন্ন রকম রূপ নিয়ে। তার নিজের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই, কিন্তু সব সময় একটা রূপ নিয়ে হাজির। আমাদের যখন যেভাবে দরকার, তিনি তখন সেই ভাবে উপস্থিত হন, তা সে চিনতে পারো বা না পারো। এমনিতে চেনা যায় না, কিন্ত যখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ঠান্ডা হয়ে যায়, অন্য কোনো সমস্যা থাকে না, কোনও কিছু নিয়েই ভাবনা নেই, শুধুই দেখার আনন্দ, তখন কিন্তু চোখের সামনে দেখা যায় তিনি কি ভাবে সঙ্গে আছেন।
বেড়াতে গিয়ে সেই জায়গায় একটা না একটা কুকুর সঙ্গী হয়নি, এরকম অভিজ্ঞতা হতে পারে না। বিশেষ করে পাহাড়ে। রাস্তায় হাঁটলে সঙ্গে একটা কুকুর জুটবেই জুটবে। সেটা প্রথম বুঝেছিলাম তপোবন বেড়াতে গিয়ে। পরে অবশ্য অন্য কিছু বুঝেছিলাম, সেটা পরে বলছি।
সেবার তপোবন যাবো বলে বাড়ি থেকে ট্রেনে উঠলাম আমরা চার জন, আমি, সঞ্জয়, বাপ্পা, আর দেবাশিস কাকু। ট্রেনে উঠে আমাদের কুপে আমার স্কুলের বন্ধু সোমেনদের আবিষ্কার করলাম। ওরা তিন জন, সোমেন, ওর ভাই, ছোটো মামা। সঙ্গে যদিও মা, বাবাও আছেন, ওঁরা গোমূখ অব্দি যাবে তাও ঘোড়ায় চড়ে। আর আমদের সাত জনেরই টার্গেট তপোবন। হরিদ্বার থেকে ভোর চারটেতে বেরিয়ে রাত আটটায় বাসে করে গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম।
জীবনে এতো কালো রাত আমি কখনো দেখিনি। বাস থেকে নেমে দেখি নিজের হাত দেখতে পাচ্ছি না, পাশের জন তো বহু দূর। পাশ দিয়ে মা গঙ্গা বয়ে চলেছে ভয়ঙ্কর রকম গর্জন করতে করতে। রাস্তা থেকেই কেউ করোও কথা শুনতে পাচ্ছি না, এমনই সেই গর্জন। হাতের টর্চ জ্বেলে সেতুর কাছে এসে মনে হলো একটা ঢেউ বা বড়ো পাথর সেতু সমেত আমাদের সেকেন্ডের ভগ্নাংশে পাউডার বানিয়ে জলে গুলে সাগর দ্বীপের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে। কাঠের পাটাতন পর পর সাজিয়ে মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ব্রিজ দুপাশের চারটে খুঁটিতে ঝুলছে, একজন হাঁটলেই সেতুটা দুলছে। তাছাড়া কোথায় পা দিচ্ছি টর্চের আলো ছাড়া দেখা অসম্ভব। আমরা এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে দোলনা সেতুর ওপর নিজের ব্যালেন্স রাখতে রাখতে দড়ি আঁকড়ে কোনো মতে লাইন দিয়ে সেতুর ওপারে ‘কালীকমলি ওয়ালা’র ধর্মশালায় উঠলাম।
একটা ইঞ্চি দশেক একটু মোটা মোমবাতির আধখানা ঘরে জ্বলছে, ভয়ঙ্কর ঠান্ডায় আমাদের আনা সব শীত পোশাক পরেও জমে যাচ্ছি। ঘরের মধ্যে এতো জোরে জল বইবার শব্দ যে দরজা জানলা বন্ধ করেও কেউ কাউকে কিছু বলতে গেলে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চিৎকার করে বলতে হচ্ছে। এসব ছাড়িয়ে আমাদের চিন্তা ওই মোমবাতি শেষ হবার আগেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পরতে হবে, কারণ এখানে প্রায় দিনই কারেন্ট আসে বটে, কিন্তু আজ আর আসবে কিনা কোনও গেরেন্টি নেই।
আমরা অনেক কষ্টে শীতকে জয় করে বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নদীর পারে খাবার হোটেলের সামনে এলাম। টর্চ নেভাতেই দেখি সূচিভেদ্য অন্ধকারে মাথার ওপর লক্ষ কোটি তারা ঝলমল করছে। তারাগুলো এতটাই উজ্জ্বল যে খানিক্ষন পরেই অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতে মনে হচ্ছে যেন এই বোধহয় তারাদের আলোয় নিজেদের ছায়া দেখতে পাবো, কিন্তু কি যেন এক বাধায় দেখতে পাচ্ছি না। এক মিনিটেই ঠক ঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করেছি, প্রচন্ড ঠান্ডা সঙ্গে ঝড়ের বেগে তীব্র তীক্ষ্ণ হাওয়া পোশাক ভেদ করে শরীরে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঠান্ডায় জমে যাবো। প্রায় দৌড়ে খাবার হোটেলে ঢুকলাম। এখানে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। টেবিলে বসে খাবো কি, খাবার শুদ্ধু হাতটা এতটাই কাঁপছে যে কিছুতেই হাতটা মুখ লক্ষ্য করে আনতে পারছি না। নাকে চোখে গলায় হাতটা কেঁপে চলে যাচ্ছে। কোনও রকমে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত ধরে মুখটাকেই হাতের কাছে নিয়ে গিয়ে দুটো রুটি রাজমার ঝোল দিয়ে খেয়ে ভেবে নিলাম ক্ষুধা নিবৃত্তি হলো। পেটে খিদে নিয়েই প্রায় দৌড়ে ঘরে চলে এলাম। আর খানিক্ষন থাকলে বোধহয় ঠান্ডায় জমে যাবো। ঘরে এসে কোনও রকমে জুতোটা খুলে সমস্ত শীতের জামা কাপড় পরেই কম্বলের তলায় ঢুকে গেলাম। আলো নিভিয়ে শুয়ে পরে যখন কাঠের দেওয়াল আর ঢালু ছাদের অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে আকাশের তারা দেখতে পাচ্ছি তখন বুঝলাম কেন ঘরের মধ্যেও এতো শীত করছে। অন্য কোথাও যাবার যখন উপায় নেই, অগত্যা খাটে শুয়ে শুয়ে তারা গুনতে গুনতে কখন যে তারার দেশে পাড়ি দিয়েছি খেয়াল নেই। সারা দিনের সমস্ত ক্লান্তি শরীরটাকে অবশ করে দিয়েছে। এক ঘুমে রাত কাবার।
সকালে ঝলমলে রোদ্দুরে গঙ্গা মায়ের মন্দিরে কপালে মেটে সিঁদুরের টিকা লাগিয়ে ‘গঙ্গা মাই কি জয়’ বলে মন্দিরের সামনে থেকে দশ টাকা দিয়ে একটা মোটা লাঠি কিনে গোমূখের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। প্রসঙ্গত বলে রাখি গোমূখ দর্শন করে ফিরে ওই লাঠি দোকানে ফেরৎ দিলে পাঁচ টাকা ফেরৎ পাবার গ্যারেন্টি ছিল, যদিও আমরা সবাই লাঠি গুলো স্মারক হিসাবে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। যাই হোক, পরিষ্কার আকাশে ঝলমলে রোদ্দুরে চড়াই উৎরাই ভেঙে হাঁটার সময় এতো গরম হচ্ছিলো যে গত রাতের প্রবল ঠান্ডাটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিলো। হাঁটার সময় পাতলা টি-শার্টটাও এমন ভাবে ঘামে ভিজে উঠছিলো যেন নিংড়ালে জল পড়বে, অথচ হাপিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে এক মিনিটের মধ্যে ঠান্ডা হওয়ার দাপটে ঘাম শুকিয়ে সমস্ত ক্লান্তি জুড়িয়ে যাচ্ছিলো। আবার নতুন উদ্যোমে হাঁটতে বেশ মজাই লাগছিলো।
সকাল আটটায় হাঁটা শুরু করে দশটা নাগাদ সাত কিলোমিটার দূরে চিরবাসায় যখন পৌঁছলাম সূর্য তখন আগুন ছোটাচ্ছে। সমুদ্র তল থেকে প্রায় বারো হাজার ফুট ওপরে সূর্যের তেজে সঙ্গে বরফের পাহাড়ে আলোর রিফ্লেকশানে যে শরীরের চামড়া পুড়ে যায় সেটা নিজে না এখানে এলে বুঝতে পারতাম না। একটা চটিতে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেবার ফাঁকে একবাটি ছোলা সুপ খেয়ে আবার হাঁটা লাগলাম ভুজবাসার উদ্দেশে। আজকের গন্তব্য ওই পর্যন্ত। এখানেই প্রথম লক্ষ করলাম একটা সাদা কালো কুকুর আমাদের সাথে চলেছে। আমরা বিশ্রাম নিতে রাস্তায় পাথরের ওপর বসলে সে আমাদের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার হাঁটতে শুরু করলেই আমাদের সাথে চলছে। তা এই অচেনা দেশে একজন বন্ধু পেলে ক্ষতি কি! রাস্তায় আমরা যখন বিস্কুট খাচ্ছি ওকেও দিচ্ছি, লজেন্স দিতে একবার শুঁকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো, বুঝলাম লজেন্স খায় না।
একদিকে হিমবাহ থেকে আসা তীব্র ঠান্ডা হাওয়া, আরেক দিকে চামড়া পোড়ানো রোদ্দুর। একদিকে প্রানান্তকর চড়াই পাথুরে রাস্তা অন্যদিকে শ্বেত মুকুট পরা হিমালয়ের অপ্রার্থিব রূপ। দুই বিপরীতমুখী পরিবেশ আমাদের একই সাথে চূড়ান্ত কষ্ট এবং অফুরন্ত আনন্দ দিচ্ছে। একটা পাহাড় টপকে যখন দেখছি সামনে আর একটা পাহাড় সেটাও টপকাতে হবে, তখন ভয়ে, ক্লান্তিতে বুক কেঁপে যাচ্ছে। আবার যতই একটা একটা করে পাহাড় টপকাচ্ছি চোখের সামনে ভাগীরথী শৃঙ্গ ক্রমশ তার রূপ উন্মুক্ত করে আমাদের আরও বেশি আকর্ষণ করে চলেছে। একটা ঘোরের মধ্যে প্রায় ছঘন্টা হেঁটে ভুজবাসার কাছে এসে পৌঁছে আমরা সবাই বসে পরে চার কিলোমিটার দূরে গোমূখের অপরূপ দৃশ্য দেখছি, দেখলাম কুকুরটা নিচে ভ্যালিতে নেমে লালবাবার আশ্রমের কাছে চলে গেলো।
আমরা লালবাবার আশ্রমে এসে জানতে পারলাম কিছুদিন আগে আগুনে মূল আশ্রম পুড়ে গেছে তাই বর্তমানে ঘোড়ার আস্তাবলকে সারিয়ে নিয়ে তীর্থ যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানেই থাকতে হবে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু ভালো শোবার জায়গা পেলে শরীর মন দুটোই তরতাজা হতো কিন্তু কিছু করার নেই। মনের দুঃখে এক রাতের জন্য ওই আস্তাবলেই আস্তানা গাড়তে হলো। কিন্তু বাইরে প্রকৃতির অপরূপ রূপ তারসাথে লালবাবার দেওয়া গরম গরম খিচুড়ি সমস্ত ক্লান্তি দূর করে শরীর, মনে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করে দিল। আর বিকাল হতেই ভাগীরথী শৃঙ্গ রং বদলের খেলায় মেতে উঠতে মনের মধ্যে যে অভাবনীয় আনন্দ ভরে উঠলো তা ভাষায় প্রকাশ করা বাতুলতা মাত্র।
পরের দিন সকালে ভুজবাসা থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে গঙ্গা নদীর উৎস গোমূখের উদশ্যে রওনা দিতেই দেখি আমাদের গতকালের সঙ্গী সেই কুকুরটা এসে হাজির। অথচ গতকাল দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যতক্ষণ আমরা ভুজবাসা ভ্যালিতে ঘুরছিলাম সে কিন্তু আমাদের কাছে একবারও আসেনি। কিন্তু মনে পড়লো সারা বিকাল কিন্তু কুকুরটা দূর থেকে আমাদের খেয়াল রেখেছিলো। কারণ অনেক বারই চোখে পড়েছিল যে আমরা যেখানেই ঘুরছি কিছুটা দূরে কুকুরটা ঘুরতে ঘুরতে কি যেন শুঁকে বেড়াচ্ছে! পাত্তা দিইনি।
এক ঘন্টার মধ্যে গোমূখে পৌঁছে গেলাম। ভাবতেই পারছি না যে গঙ্গা গোটা উত্তর ভারতকে তার প্রাণের ধারায় বাঁচিয়ে রেখেছে তার উৎস আমাদের চোখের সামনে। যে গর্ত থেকে গঙ্গা বেরিয়ে আসছে তার দিকে তাকালে সত্যিই মনে হবে একটা গরু হাঁ করে আছে আর তার মুখের মধ্যে থেকে গঙ্গা বেরিয়ে আসছে। প্রায় ঘন্টা খানেক কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম তপোবনের উদশ্যে। ভাগীরথী হিমবাহ কোনকুনি পেরিয়ে খাড়া দেয়ালের মতো পাহাড় বেয়ে আমরা উঠে চলেছি। প্রায় এক কিলোমিটারের কাছাকাছি উঠে হঠাৎ সঞ্জয় বলল, ওর খুব শরীর খারাপ লাগছে। মাথা ঘুরছে, গা বমি ভাব। তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় যা খুব স্বাভাবিক। আমরা মানে আমি, সঞ্জয় আর দেবাশিস কাকু ঠিক করলাম আমরা ফিরে যাবো, বাকিরা তপোবন চলে যাক। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিচে নামতে আরম্ভ করলাম, কারণ ওই উচ্চতায় প্রবল ঠান্ডা হাওয়ায় হাত পা যেন বেঁকে যাচ্ছে।
এইবার দেখলাম কুকুরটা কিন্তু ওদের সঙ্গে তপোবন না গিয়ে আমাদের সাথে নিচে নেমে এল। বেশ অবাক হলাম। নিচে নেমে কিন্তু পাঁচ মিনিটও বসতে পারলাম না। অপ্রতুল পোশাকে ওদের ফেরার অপেক্ষায় অন্তত দু’ঘন্টা বসে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঠান্ডায় তিনজনের শরীরই অবশ হয়ে আসছে। এদিকে আমাদেরগাইড বলে দিয়েছে কোনো অবস্থায় যেন আমরা গোমূখে ফেরার চেষ্টা না করি। কারণ হিমবাহের পাথরের নিচে ক্রিভার্স আছে যা হঠাৎ দেখে বোঝা যায় না, অসাবধানে পা পড়লেই সোজা বরফের ভেতর ঢুকে যাবে, টেনে তোলাও সবসময় সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে মৃত্যু অবধারিত। এদিকে ঠান্ডায় আমাদের কাহিল অবস্থা। দু’ঘন্টা থাকলে এমনিই মরে যাবো। তারচেয়ে বরং ফেরার চেষ্টা করা যাক, কপালে থাকলে বেঁচে যাবো। না হলে মৃত্যু তো দেখতেই পাচ্ছি।
হিমবাহে হাঁটার নিয়ম হল অভিজ্ঞ লোকেরা আগে যেতে যেতে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে নিশানা করে যায় আর অনভিজ্ঞরা সেই নিশানা দেখে এগোতে থাকে। তাতে ক্রিভার্স-এ পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। যাবার সময় আমাদের গাইড সেই নিশানা গুলো দেখিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু প্রায় দু’কিলোমিটার রাস্তায় একবার দেখে সব নিশানা চিনে রাখা সম্ভব নয়। তাই ফেরার সময় আমরা একটা নিশানার সামনে দাঁড়িয়ে পরেরটা খুঁজে এগোতে লাগলাম। কিন্তু কিছুটা গিয়ে খেই হারিয়ে নিশানাগুলো চিনতে বা বুঝতে পারছিলাম না। ফলে প্রথমে ভয় পেয়ে গেলেও বাধ্য হয়ে কপালের ওপর ভরসা করে এগোতে শুরু করতেই দেখি কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। এতক্ষন ও আমাদের সাথে থাকলেও কখনোই পাত্তা দিইনি কিন্তু এখন দেখলাম ওই আমাদের উদ্ধার কর্তা হয়ে অবির্ভুত হলো। কুকুরটা একটু করে যাচ্ছে আর পেছন ফিরে দেখছে আমরা ঠিক আসছি কিনা। একটু এদিক ওদিক পাথরে পা দিলেই দাঁড়িয়ে পড়ে ঘেউ ঘেউ করে বকছে। আর ও যে পাথর গুলো দিয়ে আসছে সেগুলিতে আমরা পা দিয়ে এলে নিশ্চিন্তে আরও খানিকটা এগিয়ে পেছন ফিরে দেখছে আমরা ঠিক আসছি কিনা।
এই ভাবে নিশ্চিন্তে গোমূখে ফিরে এসে এক সাধুবাবার কাছে জানতে পারলাম গত তিন বছরে বাইশ জন ক্রিভার্স-এ তলিয়ে গেছে গাইডের কথা না শুনে নিজেদের মতো করে যেতে গিয়ে। এদিকে কুকুর রূপে ঈশ্বর বকে-ধমকে আমাদের সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করলো।
লেখক পরিচিতি : উজ্জ্বল চ্যাটার্জি
উজ্জ্বল চ্যাটার্জী একজন শখের লেখক। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত লেখা প্রকাশ করেন ও আনন্দমেলা ও বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প , কবিতা প্রকাশ হয়